একটি্ বিশেষ নিবন্ধ
মা হা বু বু ল হা সা ন নী রু
ফুটবল এদেশের মাটি ও মানুষের প্রাণের খেলা। ফুটবলের নামে এদেশের মানুষের রক্তে নাচন লাগে, প্রাণে উৎসব জাগে। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এই দেশটির টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া- কোথায় নেই ফুটবলের প্রতি মানুষের গভীর ভালোবাসা? নানা কারণে যদিও আজ এদেশের ফুটবল সংকটাপন্ন, কিন্তু বিশ্বকাপ ফুটবল তো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, এদেশে ফুটবলের কী অসম্ভব জনপ্রিয়তা! সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপ ফুটবলের কথাই ধরুন। বিশ্বকাপকে ঘিরে এদেশের আমজনতার সে কী উৎসাহ-উদ্দীপনা, উত্তাপ-উত্তেজনা! রাত জেগে খেলা দেখার কতো আয়োজন! প্রিয় দলের পতাকায় ছেয়ে গিয়েছিলো গোটা দেশ। বিশ্বকাপ চলাকালীন একটি মাস সারা দেশ কেঁপেছিলো ফুটবলের শ্লোগানে। আড্ডা-আলোচনার মূল বিষয় ছিলো ফুটবল।
এদিকে এ বছর পেশাদার লীগ চালুর মধ্য দিয়ে আমাদের মৃতপ্রায় ফুটবল গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু যথাযথ পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় প্রচার প্রচারণার অভাবে এ ফুটবল সেভাবে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারছে না। এ বছর প্রথম পেশাদার ফুটবল লীগ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলতে গেলে দর্শকশূন্য মাঠে। প্রথম পেশাদার ফুটবল লীগের শিরোপা জয় করেছে আবাহনী ক্রীড়াচক্র। তবে পেশাদার লীগের সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে সব কথা বলার সময় এখনো আসেনি। কিন্তু যা সত্যি তা হলো, এ লীগ সম্পর্কে বাফুফে আরো বেশী সচেতন না হলে এর ভবিষ্যতও তেমন মঙ্গলময় হবে না।
এদেশে ফুটবলের জনপ্রিয়তা আজও গগণচুম্বী। বিগত দিনে শহর থেকে গঞ্জ-গ্রাম কোন্ মাঠেই বা না বসতো ফুটবলের উৎসব? একসময় ঢাকা লীগ বা ফেডারেশন কাপের লড়াইকে ঘিরে কী মাতোয়ারাই না হয়ে উঠতো সারাদেশ! খেলোয়াড়দের পায়ে-বলে আগুন আর স্টেডিয়ামভরা দর্শকের উল্লাস-উত্তেজনা- মহান ফুটবলের সে কী মোহনীয় রূপ! হৃদয় ছোঁয়া আহবান! ফুটবলের সেই প্রতিযোগিতা আজ নেই, কিন্তু দেশের মানুষের রয়েছে ফুটবলের প্রতি প্রবল টান, প্রগাঢ় ভালোবাসা। চলুন না একটু হাঁটা যাক এই কালজয়ী ফুটবলের এ দেশীয় ইতিহাসের পথ ধরে।
তবে শুরুতেই একটা কথা বলে নেই, আমাদের ‘অতীত’ নামের পুরনো তোবড়ানো ট্রাঙ্কের ভেতোরে গড়ে ওঠা উঁই-ইঁদুর আর আরশোলার রাজত্ব থেকে ইতিহাসকে উদ্ধার করা খুব সহজ কাজ নয়। তা যেকোনো ক্ষেত্রের কথাই বলা হোক না কেনো। ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণে আমাদের অনীহা আর অবহেলার কথা কার না জানা। ইতিহাস-ঐতিহ্য লালন কিংবা সংরক্ষণে এ জাতির কার্পণ্য বা আলস্যের জুড়ি নেই। অতীতকে ‘অতীত’ বলে কালের গর্ভে চালান করে দিতে আমরা পটু। ফলে কোনো ক্ষেত্রে ইতিহাস ঘাটতে গেলে একেবারে যেনো অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে হয়। রাষ্ট্রীয় কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ইতিহাস সংরক্ষণের মানসিকতা নেই বলে, যারা ইতিহাস-ঐতিহ্যের সন্ধানে পা বাড়ান, তাদের পড়তে হয় দুঃখজনক অন্ধদশায়। পরে ছুটতে হয় প্রবীণ, কিংবা বোদ্ধা বা জানা শোনা এর ওর কাছে, অথবা কড়া নাড়তে হয় সংগ্রাহকদের দ্বারে, কিংবা ঝুঁকতে হয় পুরনো দিনের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাতায়। এ লেখাটি লিখতে গিয়ে আমাকে আমাদের ফুটবলের ইতিহাসের অনেক বাঁকে থমকে যেতে হয়েছে। কখনো তথ্য যোগাড় করতে গিয়ে অপ্রতূলতা বা অসংলগ্নতার কারণে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়েছে। আবার একই ঘটনার বিভিন্ন সূত্রে অভিন্ন চিত্র বা বর্ণনা না পাবার ফলে বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়েছে। তারপরও যতোটা সম্ভব চেষ্টা করেছি সঠিক তথ্য তুলে এনে লেখাটিতে নির্ভূল তথ্য উপস্থাপন করতে। এরপরও যদি কোনো কারণে লেখাটির কোথাও কোনো দুর্বলতা কিংবা ত্রুটি চোখে পড়ে, বা যদি কোনো কৃতি ফুটবলার অথবা সংগঠকের নাম বাদ পড়ে থাকে – সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের নির্ভুল তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার সবিশেষ অনুরোধ রইলো। নির্ভুল, নিখুঁত ইতিহাস সংরক্ষণ এবং লালনই হোক আমাদের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার।
উ প ম হা দে শে ফু ট ব লে র আ বি র্ভা ব
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) প্রথমেই আলোকপাত করা যাক, উপমহাদেশে কেমন করে এলো এই বরেণ্য ফুটবল। আর কেমন করেই বা সে করলো এ অঞ্চলের মানুষের হৃদয়। একটি বিদেশী খেলা হওয়া সত্ত্বেও কি করে খেলাটা মিশে গেলো এদেশের মাটি ও মানুষের মাঝে? কেমন করেই বা বিজয় রথ উড়িয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো নগর-বন্দর, গ্রামে-গঞ্জে? কি জানতে ইচ্ছে করে না সে ইতিহাস?
প্রথমেই আলোকপাত করা যাক, উপমহাদেশে কেমন করে এলো এই বরেণ্য ফুটবল। আর কেমন করেই বা সে করলো এ অঞ্চলের মানুষের হৃদয়। একটি বিদেশী খেলা হওয়া সত্ত্বেও কি করে খেলাটা মিশে গেলো এদেশের মাটি ও মানুষের মাঝে? কেমন করেই বা বিজয় রথ উড়িয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো নগর-বন্দর, গ্রামে-গঞ্জে? কি জানতে ইচ্ছে করে না সে ইতিহাস?
এই উপমহাদেশে ফুটবলের আবির্ভাব সম্পর্কে জানা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে গঙ্গার ঘাটে নোঙ্গর করা দু’টো বিলেতি জাহাজে করেই এসেছিলো ‘ফুটবল’ নামের এই আজব খেলার বীজ। একদিন সকালবেলার সোনারোদ ছড়িয়ে পড়া একটি পুরনো কেল্লার মাঠে জাহাজের ফুটবল নিয়ে নামলো বিলেতি নাবিকরা । তারা যখন ফুটবল খেলছিলো তখন কেল্লার সৈনিকদের চোখ তো ছানাবড়া। এ আবার কি খেলা রে বাবা! তারা নাবিকদের খেলা দেখতে লাগলো অবাক চোখে এবং একসময় নিজেরাও যোগ দিলো নাবিকদের সাথে। লাথি মারলো ফুটবলের গায়ে। উপমহাদেশে এই হলো কালজয়ী ফুটবলের গোড়াপত্তন। এটা হচ্ছে লোকমুখে চালান হয়ে আসা একটা অলিখিত ইতিহাস। কাগজে-কলমে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে নথিপত্র ঘাটলে দেখা যায়, এসপ্লানেড ময়দানে ১৮৫৪ সালের এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রথম ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলাটিতে কলকাতার শীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষদের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন ব্যারাকপুরের ইংরেজ সাহেবরা। এ খেলায় অংশ নেয়া দল দু’টির একটির নাম ছিলো ‘ক্যালকাটা অফ সিভিলিয়ানস’ আর অপরটি ‘জ্যান্টলম্যান অফ ব্যারাকপুর’। এই খেলাটির পর পরবর্তী ১৪ বছর আর ফুটবলের কোনো অস্তিত্ব নথিপত্রে মেলে না। এরপর আবার ফুটবলের সাক্ষাৎ মেলে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর। সিপাহী বিদ্রোহের জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড থেকে বেড়িয়ে ইংরেজরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আবার খেলাটির দিকে মনোযোগ দেয়। বলা যায়, এখান থেকেই ফুটবল উপমহাদেশে তার জয়যাত্রা শুরু করে।
১৮৬৮ সালে এসপ্লানেড ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো এক প্রীতি ম্যাচ। এতে ‘আইসিএস’দের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বিদ্যালয় ইটনের সাবেক ছাত্রদের নিয়ে গঠিত ‘হটোনিয়াস ক্লাব’। এ খেলায় হটোনিয়াস ৩-০ গোলে জয়লাভ করে। হটোনিয়াস ক্লাবের হয়ে চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন খোদ কলকাতার সে সময়ের গভর্ণর রবার্ট ভ্যানসিটার্ট। তিনি একাই ২টি গোল করেন । অপর গোলটি করেন ডব্লু এইচ ট্রান্ট।
দু’বছর বন্ধ থাকার পর ১৮৭০ সালে আবার ফুটবল শুরু হলো এসপ্লানেট মাঠে। এ সময় লড়াই হতো পাবলিক স্কুল হ্যারো, ইটন, উইনচেস্টারের ছাত্রদের সাথে প্রাইভেট স্কুল মিসটিনার ছাত্রদের। এদের খেলা দেখার পর খেলাটি খেলতে বেনিয়া সাহেবদেরও সাধ জাগে। তারা দল গঠন করে খেলতে নামে এবং প্রথম খেলাতেই হেরে যায় আইসিএস-এর কাছে।
বলাবাহুল্য, ব্রিটিশ সম্রাজ্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিলো বলে সে সময় কলকাতার বন্দরে ভিড়তো বড় বড় জাহাজ, আর এসব জাহাজের নাবিকদের সাথে কেল্লার সেনাদের ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতো।
১৮৭২ সালে গঠিত হয় এক ফুটবল ক্লাব। যে ক্লাবের খেলোয়াড়রা ফুটবল খেলতো অনেকটা রাগবির মতো করে। জানা যায়, শুধু ফুটবল খেলার জন্য ট্রেডস ক্লাব নামে একটি ক্লাব গড়ে ওঠে ১৮৭৮ সালে। উদ্যোগটা ছিলো ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের। সে সময় ডালহৌসী ইনস্টিটিউট ছিলো ক্যালকাটা ট্রেডস এসোশিয়েশনের প্রধান কর্মস্থল। আর যার কারণে পরে ট্রেডস ক্লাবটি ডালহৌসী ক্লাবে রূপান্তরিত হয়। ইতিমধ্যে ফুটবল তার কালজয়ী আলোকমালার সূচনা করে ছড়িয়ে পড়তে থাকে সরকারী ও মিশনারী স্কুলগুলোতে। এ সময় শিক্ষিত বাঙালীরা ফুটবলের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। ১৮৭৯ সালে মি. বি ভি গুপ্ত নামের এক ভদ্রলোক গড়ে তোলেন প্রেসিডেন্সি কলেজ ক্লাব। শুরুতে ক্রিকেটের প্রতি এই ক্লাবের ঝোঁক থাকলেও পরবর্তীতে এরা ফুটবলও খেলতে শুরু করে। নথিপত্রে পাওয়া যায়, ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের বাঙালী ছাত্ররাই প্রথম ফুটবল খেলে। আর এ আয়োজনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্ট্যাক নামের এক অধ্যাপক। তিনি গাঁটের পয়সা খরচ করে ফুটবল কিনে এনে ছাত্রদের মাঠে নামান। এ বছরই গঙ্গার এপাড়ে ‘নেভাল ভলান্টিয়ার্স ক্লাব’ আর ওপাড়ে ‘হাওড়া ইউনাইটেড ক্লাব’ গড়ে ওঠে। ‘নেভাল ভলান্টিয়ার্স ক্লাব’ পরে অবশ্য ‘ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব’ নাম ধারণ করে। আর্মেনিয়ানরাও তখন একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে। এ সময়টাতে বিভিন্ন কলেজে ফুটবলের প্রসার বাড়তে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ। যদিও এসব কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বাঙালী ছিলো না বললেই চলে।
দিন বদলের সাথে সাথে ফুটবলও গড়াতে থাকে সোনালী অধ্যায় রচনার লক্ষ্যে। সে সময় ফুটবল সাধারণদের কাছে সাহেবী খেলার মর্যাদা পেতো। স্বভাবতই নিজেদের মর্যাদার পরিধি বাড়াবার জন্য কলকাতার নব্য বাবুরা এই খেলার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। সাহেবী ঢঙ্গে জীবন যাপনে অভ্যস্ত শোভাবাজারের রাজপরিবারের সদ্যরা ১৮৮৫ সালে গড়ে তোলেন ‘শোভাবাজার ক্লাব’- যা প্রথম বাঙ্গালী ক্লাব হিসেবে স্বীকৃত। এরপর জন্ম নেয় ‘কুমারটুলি ক্লাব’। ১৮৮৪ সালে কলেজ ছাত্রদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠলো ‘ওয়েলিংটন ক্লাব’। পরে এই ক্লাবের সদস্যদের একটা অংশ অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে বিভক্ত হয়ে গড়ে তোলে ‘টাউন ক্লাব’। এ সময় দক্ষিণ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ন্যাশনাল ক্লাব’।
দিনবদলের সাথে সাথে ফুটবলের রঙ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো উপমহাদেশের মানুষের অন্তরে। ফুটবল খেলতে নেমে অন্যরকম একটা আনন্দ আর মজা পাওয়ার কারণে খেলাটির জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়তে থাকে। ঘটতে থাকে এর প্রসার। আর কলকাতায় ফুটবলের এ প্রসারে আরো বেশী উৎসাহী হয়ে ওঠে ইংলিশ বনিকরা। সে আমলে অর্থাৎ ১৯৮৯ সালে পাঁচশত টাকা দিয়ে একটি কাপ বানিয়ে তারা শুরু করে ‘ট্রেভস কাপ’-এর প্রতিযোগিতা। অবশ্য এ প্রতিযোগিতা বলতে গেলে সাদা চামড়াদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলো। কেননা একমাত্র শোভাবাজার ছাড়া এ আয়োজনে আর কোনো বাঙালী ক্লাব খেলার অনুমতি পায়নি। ট্রেভস কাপ-এর প্রথম শিরোপা জয় করে ডালহৌসী ক্লাব। এরপর ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে সেন্ট জেভিয়াস কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও শিবপুর কলেজ এই কাপ জয় করে। কুচবিহারের মহারাজার উদ্যোগে ১৮৯৩ সালে চালু হয় ‘কুচবিহার কাপ’। এর পরের বছর ইংলিশ ছাত্রদের জন্য ‘ক্যাডেট কাপ’ আর বাঙালী ছাত্রদের জন্য ‘এলিয়ট শিল্ড’ প্রবর্তিত হয়। ১৮৯৮ সালে প্রথম বিভাগ লীগ চালু হলেও ১৯১৬ সাল পর্যন্ত এ লীগে কোনো ভারতীয় দল খেলার সুযোগ পায়নি। তবে সেকেন্ড ডিভিশনে দু’টি বাঙালী দল মোহনবাগান ও এরিয়ান ক্লাব খেলার সুযোগ পেতো।
অপর একটি সূত্রমতে, উপমহাদেশে বড় মাপের একটি প্রতিযোগিতা চালানোর জন্য ১৮৯৩ সালে গড়ে তোলা হয় ‘ইন্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন’, যা ‘আইএফএ’ নামে পরিচিত। এই এসোসিয়েশনই একই বছর শুরু করে ‘আইএফএ শিল্ড’ প্রতিযোগিতা। জানা যায়, এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ছিলেন জার্মান সাহেব স্যার এ.এ আপকার, ইংরেজ সাহেব জে সাদারল্যান্ড এবং কুচবিহার ও পাতিয়ালয়ের দুই মহারাজ। শিল্ডটি তৈরী করে কলকাতার ওয়াল্টার লক কোম্পানীর মাধ্যমে লন্ডনের বিখ্যাত এলকিংটন কোম্পানী। আর এ শিল্ডের গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন ক্লাব, গোরা সৈন্যদের দল এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে।
উনিশ শতকে ফুটবল মূলত সাহেব ও তাদের সেনা ছাউনীর সীমানাবন্দী থেকে কচ্ছপ গতিতে এগিয়েছে। এখানে ভারতীয়দের বঞ্চনারও একটা করুণ ইতিহাস আছে। বর্ণবিদ্বেষী ইংরেজরা নিজেদের খেলা বলে ফুটবল থেকে ভারতীয়দের যতোটা পারতো দূরে ঠেলে দিতো। তবে তা সত্ত্বেও এই খেলাটি দিনে দিনে শ্বেতাঙ্গ বাবুদের সেই সীমানার দেয়াল টপকে ধরা দেয় ভারতীয়দের কাছে। ক্রমে ক্রমে ফুটবলকে ঘিরে গড়ে ওঠে ছোট-বড় ক্লাব। একথা তো সকলেরই জানা যে, বৃটিশ শাসনামলে এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-খেলাধুলা সবকিছুই ছিলো হিন্দুদের দখলে। আর তাদের এই আধিপত্যের মুখে মুসলিম সম্প্রদায় ছিলো বড়ই অসহায়। আর যার কারণে বৃটিশদের পর ফুটবল ছিলো হিন্দুদের পায়ে। উনিশ শতকের শেষ দশকে জন্মলাভ করা কলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ফুটবলকে মুসলিম শিবিরে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। কারো কারো মতে, এ ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই তৎকালীন বাংলার পূর্বাঞ্চলে ফুটবলের ফরোয়ার্ড মার্চ শুরু হয়। দিনে দিনে এই অঞ্চলের অনেক স্থানে মোহামেডানের বহু ইউনিট জন্ম নেয়। গেলো শতাব্দীর বিশের দশকে প্রতিষ্ঠিত অনেক ইউনিটের একটি হচ্ছে কুমিল্লা মোহামেডান। শুধু কি তাই, সে সময়ে মুসলমানের রাজনৈতিক উথ্থানের পেছনেও রয়েছে ফুটবল এবং এই ক্লাবের একটা বিশেষ ভূমিকা। বৃটিশদের কু-শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে যখন ভারতীয়দের মধ্যে আন্দোলন দানা বাঁধছিলো, ভারতীয় রাজনীতির তাওয়া যখন ক্রমেই উত্তপ্ত হচ্ছিলো সে সময় নবাবজাদা আজিজুল ইসলাম ফুটবলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে এবং মুসলমান সমাজকে ফুটবলের প্রতি আকৃষ্ট করতে অর্থাৎ ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন জুবিলী ক্লাব। পরে এই ক্লাবটির নাম দু’বার পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে ক্রিসেন্ট ক্লাব ও পরে হামিদিয়া ক্লাব। এই ক্লাবটি সর্বশেষ ১৮৯১ সালে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব নামধারণ করে নতুন পথে যাত্রা শুরু করে। তবে প্রথম দিকে এ যাত্রা পথ কুসুমাচ্চীর্ন ছিলো না। বরং বলা যায় প্রবল প্রতিকূলতা তাকে গ্রাস করে। বিশেষ মহলের রক্তচক্ষু আর আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে শুধু নামের অস্তিত্ব নিয়েই ক্লাবটিকে চলতে হয় প্রায় তিনটি দশক। মূলত এরপরই শুরু হয় অবিস্মরনীয় ইতিহাস রচনার পালা।
আমরা মুখে যতোই বলি না কেনো যে, খেলাধুলার সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। বাস্তব সত্যি হচ্ছে, ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজনীতির একটা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব সবসময় ছিলো, এখনো আছে। গত শতাব্দীর বিশের দশক থেকেই ভারতবর্ষে কংগ্রেস, খেলাফত আন্দোলন, চট্রগামের অস্ত্রাগার লুটসহ উত্তপ্ত নানা রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রেক্ষাপটে হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায় স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবীতে যখন সোচ্চার হয়ে ওঠে সে সময় কলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব কলকাতা ফুটবল লীগের দ্বিতীয় বিভাগ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথম বিভাগে উন্নীত হয় এবং এখান থেকেই শুরু হয় তাদের লাগাতার বিজয় যাত্রা। ’৩৫ থেকে ’৩৮ টানা পাঁচ বছর এই ক্লাবটি কলকাতা লীগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করলে মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরনের সৃষ্টি হয়। এবং মুসলমানদের এই নবজাগরণ তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনকে বেগবান করতে বিশেষ ভুমিকা রাখে। অপরদিকে মোহামেডানের এই অভূতপূর্ব সাফল্যে ঈর্ষান্বিত মৌলবাদী হিন্দু সম্প্রদায় বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা সোচ্চার হয়ে ওঠে মোহামেডান তথা মুসলমানদের অগ্রগতি রুখতে। এ লক্ষ্যে তাদের একটা অংশ নানা অপকর্ম এবং অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়। তারা ক্লাবটির বিরুদ্ধে ইংরেজদেরও ক্ষেপিয়ে তোলে। এক সময় ইংরেজরা ক্লাবটিকে ‘ইংরেজ বিরোধী ঘাঁটি’ হিসেবে চিহিৃত করে এর খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের ওপর নানা নির্যাতনের মাধ্যমে দমন নীতি প্রয়োগ করে। জানা যায়, বৃটিশদের কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এই মোহামেডান ক্লাবে একবার আশ্রয় নিয়েছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এখানে আত্মগোপন করে থাকার সময় তিনি মোহামেডানকে নিয়ে একটা গানও লিখেছিলেন। নজরুলের প্রসঙ্গ যখন এলোই তখন এখানে তার আর একটি পরিচয়ের কথা না বলে পারছি না। আমার ধারণা, নজরুলের এ পরিচয়টা অনেকেরই অজানা। নজরুলও একসময় ফুটবল জগতের একজন ছিলেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে মুসলমানদের প্রথম পত্রিকা সওগাত-এর সম্পাদক নাসিরউদ্দিনের মুখোমুখি হয়েছিলাম একাধিকবার। সে সাক্ষাৎকারে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে স্মৃতিচারণকালে নাসিরউদ্দিন বলেছিলেন, ‘নজরুলের বয়স যখন ৭/৮ বছর তখন তার সঙ্গে আমার পরিচয়। নজরুলকে আমি ফুটবল এবং দাবা খেলতে দেখেছি। তবে ও আড্ডা মারতে বেশী পছন্দ করতো। আবার অনেক সময় দেখা যেতো বল নিয়ে সারাদিন মাঠে পার করে দিতো। এ সময় সে খাওয়া-দাওয়ার কথাও ভুলে যেতো।’ আর নিজের ফুটবল খেলা সম্পর্কে এই বরেণ্য ব্যক্তিত্ব বলেছেন, ‘মাঝে মাঝে আমিও ফুটবল খেলতাম, তবে আমাদের সময়টাতে ফুটবল ছিলো অনেকটা দুর্লভ আর যার কারণে আমরা আশেপাশের গ্রামের ছেলেরা মিলে জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলতাম।’ এ সময় সওগাত সম্পাদক ফুটবল খেলতে গিয়ে তাঁর একটি মজার ঘটনার বর্ণনা দেন এভাবে-‘ আমরা ক’জন ছেলে জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলছিলাম। অনেক চেষ্টা করেও আমি গোল করতে পারছিলাম না। যখন পায়ের কাজে ব্যর্থ হলাম তখন হঠাৎ করেই জাম্বুরাটা হাত দিয়ে তুলে গোলবারের ভেতোরে ছুঁড়ে মারলাম। গোল হলো। কিন্তু কোনো খেলোয়াড়ই আমার সে গোল মেনে নিতে চাইলো না। শেষ পর্যন্ত হৈ চৈ আর তর্কাতর্কির মধ্য দিয়ে সেদিনের খেলা শেষ হলো।’
সে যাই হোক, মুসলিম সমাজে ফুটবলের জাগরণের স্রষ্টা কলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব বিভিন্ন সময়ে নানা বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হলেও সাফল্যের ঝান্ডা কখনোই তাদের হস্তচ্যুত হয়নি। গত শতকের সত্তর দশক পর্যন্ত এই দলটি ভারতীয় ফুটবলে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করে ছিলো। আজ অবশ্য সেই টগবগে যৌবন নেই।
ঢা কা র ফু ট ব ল লী গ
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) ঢাকার ফুটবল লীগ শেষ হওয়ার পর পত্র-পত্রিকায় লীগের যে ‘রোল অব অনার’ প্রকাশ করা হয়, তাতে দেখা যায়, ঢাকার ফুটবল লীগের প্রথম আসর বসেছিলো ১৯৪৮ সালে। তবে এই তথ্য যে ঠিক নয়, সেটা ইতিহাস ঘাঁটলেই বেড়িয়ে পড়ে। কোথাও কোথাও পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, এরও অনেক আগে শুরু হয়েছিলো ঢাকার ফুটবল লীগ। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার ঈদসংখ্যায় মুদ্রিত একটি নিবন্ধে একটি ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছিলো এভাবে- ১৯২৯ সালে ঢাকার নবাব পরিবারের এক সন্তান ঢাকার ফুটবল লীগে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের মধ্যে জাকাত বন্টন করতে গিয়ে খেলোয়াড়দের দ্বারা আক্রান্ত হন। খেলোয়াড়দের কারো কারো ভাগে টাকা কম পড়াতে তারা নবাব পরিবারের সেই সদস্যকে আক্রমন করে। খবর পেয়ে নবাব বাড়ির গার্ডরা খেলোয়াড়দের ওপর পাথর ছুঁড়ে আহত সদস্যকে উদ্ধার করে। উল্লেখ্য, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেবার পুরনো ঢাকায় ঈদ উৎসব পালিত হয়েছে অত্যন্ত ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে।
ঢাকার ফুটবল লীগ শেষ হওয়ার পর পত্র-পত্রিকায় লীগের যে ‘রোল অব অনার’ প্রকাশ করা হয়, তাতে দেখা যায়, ঢাকার ফুটবল লীগের প্রথম আসর বসেছিলো ১৯৪৮ সালে। তবে এই তথ্য যে ঠিক নয়, সেটা ইতিহাস ঘাঁটলেই বেড়িয়ে পড়ে। কোথাও কোথাও পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, এরও অনেক আগে শুরু হয়েছিলো ঢাকার ফুটবল লীগ। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার ঈদসংখ্যায় মুদ্রিত একটি নিবন্ধে একটি ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছিলো এভাবে- ১৯২৯ সালে ঢাকার নবাব পরিবারের এক সন্তান ঢাকার ফুটবল লীগে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের মধ্যে জাকাত বন্টন করতে গিয়ে খেলোয়াড়দের দ্বারা আক্রান্ত হন। খেলোয়াড়দের কারো কারো ভাগে টাকা কম পড়াতে তারা নবাব পরিবারের সেই সদস্যকে আক্রমন করে। খবর পেয়ে নবাব বাড়ির গার্ডরা খেলোয়াড়দের ওপর পাথর ছুঁড়ে আহত সদস্যকে উদ্ধার করে। উল্লেখ্য, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেবার পুরনো ঢাকায় ঈদ উৎসব পালিত হয়েছে অত্যন্ত ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে।
এদিকে পুরনো ঢাকার লোকমান নামের এক বাসিন্দা তার স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে- ‘আমার দাদা পাকিস্তান মাঠে (বর্তমানে বাংলাদেশ মাঠ) অনুষ্ঠিত ঢাকা ফুটবল লীগের দর্শক ছিলেন। সে সময় লীগে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ছিলো কম। পাঁচ থেকে ছ’টা। আর দলগুলোর অধিকাংশ খেলোয়াড়ই ছিলো ইংরেজ। দলে খেলোয়াড় হিসেবে নাম থাকলেও হিন্দু ও মুসলমানেরা মূলত ইংরেজ ফুটবলারদের সাজ-সরঞ্জাম বহন করতো।’ পুরনো ঢাকার বাসিন্দা লোকমানের ভাষ্য মতে, ‘যে দল লীগে চ্যাম্পিয়ন হতো তাদের সাত রাত বাঈজীদের সাথে ফুর্তি করার অনুমতি দেয়া হতো।’
আবার ঢাকার ওয়ারী ক্লাবের গোড়ার ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই ঢাকায় নিয়মিত ফুটবল লীগ অনুষ্ঠিত হতো। কলকাতায় ফুটবল চালু হওয়ার কিছুদিন পরই তা চলে আসে ঢাকায়। তখন একে বলা হতো ‘কলকাত্তাইয়া ফ্যাশন’। ফুটবলে লাথি মেরে বেশ মজা পায় এ অঞ্চলের তরুণরা। তারা এ খেলার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে একদিকে যেমন খেলোয়াড় বাড়তে থাকে অপরদিকে বাড়তে থাকে দর্শক। ক্রমেই খেলাটি পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় চালু হয়ে যায়। একের পর এক স্কুল-কলেজগুলোর মাঠ ফুটবলের দখলে চলে যেতে থাকে। গড়ে ওঠে বিভিন্ন দল। শুরু হয় ফ্রেন্ডলি ম্যাচের প্রচলন। এক এলাকার দল আর এক এলাকায় গিয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতো। ঠিক এ সময় ফুটবলের জনপ্রিয়তার কথা বিবেচনা করে একটি নিয়মিত ফুটবল লীগ চালু করতে এগিয়ে আসেন ঢাকার কয়েক বিত্তশালী। সেটা উনিশ শতকের গোড়াতেই। এ সময় ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ও ওয়ারী ক্লাবই ছিলো প্রধান দু’টো দল। সে আমলে এই ক্লাব দু’টো শুধু ঢাকাতেই নয়, কলকাতাতেও আলোচনার ঝড় তোলে। ঢাকা এবং কলকাতার মাঠে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন দলের বিরুদ্ধে নৈপুণ্যপূর্ণ ফুটবল প্রদর্শন করে দর্শকদের নজর কাড়ে এ দু’টি দল। এদের মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে ঢাকার ফুটবলের সুনাম। সে সময় এই ক্লাব দু’টোতে খেলতো একঝাঁক কৃতি ফুটবলার। যাদের নাম ঘুরে বেড়াতো মানুষের মুখে মুখে।
১৯১৫ সালে শক্তিশালী কাস্টমসের বিরুদ্ধে আইএফএ শিল্ডে পর পর দু’দিন ড্র করার পর তৃতীয় দিন পরাজিত হলেও ওয়ারী ক্লাবের ফুটবল নৈপুণ্য কলকাতার মানুষের মুখে মুখে প্রশংসিত হয়। ১৯১৭ সালে এই ওয়ারী ক্লাব সে সময়ের লীগ চ্যাম্পিয়ন ইংরেজ দল লিংকসকে পরাজিত করে চমকে দেয় সকলকে। এর পরের বছরই তারা হারায় কলকাতার অন্যতম শক্তিশালী দল মোহনবাগানকে। সে সময়ে মোহনবাগানকে হারানো খুব সহজ কথা ছিলো না। এ খেলায় ওয়ারীর অধিনায়ক ছিলেন কানু রায়। ১৯২৫ সালে আইএফএ শিল্ডের প্রথম খেলায় ওয়ারী শক্তিশালী শেরউডের সাথে তুমুল লড়াই করার পর দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১-২ গোলে হেরে যায়। ওয়ারীর এ লড়াইয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে সে সময়ের ইংলিশ পত্রিকাগুলোও । এরপর ১৯২৯ সালে কলকাতায় সফররত ভুটানের রেঙ্গুন ক্লাবের সাথে খেলাটি ১-১ গোলে অমিমাংসিত থাকলে পরের দিন গড়ায়, তবে পরের দিন বৃষ্টির কারণে ওয়ারীর কপাল পোড়ে। এ খেলায় তারা তিন গোলে হেরে যায়। অর্থাৎ এ সব ঘটনা প্রবাহ থেকেই বোঝা যায়, ১৯৪৭ নয়, ঢাকার লীগ তারও অন্তত ৩৫ থেকে ৪০ বছর আগে মাঠে গড়িয়েছে।
ঢা কা র ফু ট ব লা র
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) সে আমলে কেমন ছিলো ঢাকার ফুটবল? কেমন খেলতো ঢাকার ফুটবলাররা? এ সব প্রশ্নের উত্তর কোন্ ফুটবলামোদীরইবা জানতে না ইচ্ছে করে? ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায়, ঢাকার তারুণ্য ফুটবলে লাথি মারার পর থেকেই উদ্ভাসিত। গোড়া থেকেই মাঠে তাদের নৈপুণ্য ছিলো চোখে পড়ার মতো। ঢাকার ছেলেরা যেখানেই খেলতে গেছে সেখানেই প্রশংসিত হয়েছে তাদের ফুটবল নৈপুণ্য। গড়ে উঠেছে অসংখ্য ভক্ত-সমর্থক। এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়, কলকাতায় গিয়ে ঢাকার ছেলেরা যখন একের পর এক খেলায় চমকপ্রদ নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে থাকে তখন কলকাতায় গড়ে ওঠে ঢাকার ফুটবলের বিশাল প্রেমিক গোষ্ঠী। আর পরে এদেরই উৎসাহ অনুপ্রেরণায় পূর্ববঙ্গের ছেলেদের নিয়ে গঠিত হয় ‘ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব’। ঢাকার ওয়ারী ক্লাব থেকে এ সময় দীনেশ গুহ, ভোলা, ভানু দত্ত রায়, প্রশান্ত, পোদ্দার- প্রমুখ ফুটবলার ইস্ট বেঙ্গলে যোগ দেন।
সে আমলে কেমন ছিলো ঢাকার ফুটবল? কেমন খেলতো ঢাকার ফুটবলাররা? এ সব প্রশ্নের উত্তর কোন্ ফুটবলামোদীরইবা জানতে না ইচ্ছে করে? ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায়, ঢাকার তারুণ্য ফুটবলে লাথি মারার পর থেকেই উদ্ভাসিত। গোড়া থেকেই মাঠে তাদের নৈপুণ্য ছিলো চোখে পড়ার মতো। ঢাকার ছেলেরা যেখানেই খেলতে গেছে সেখানেই প্রশংসিত হয়েছে তাদের ফুটবল নৈপুণ্য। গড়ে উঠেছে অসংখ্য ভক্ত-সমর্থক। এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়, কলকাতায় গিয়ে ঢাকার ছেলেরা যখন একের পর এক খেলায় চমকপ্রদ নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে থাকে তখন কলকাতায় গড়ে ওঠে ঢাকার ফুটবলের বিশাল প্রেমিক গোষ্ঠী। আর পরে এদেরই উৎসাহ অনুপ্রেরণায় পূর্ববঙ্গের ছেলেদের নিয়ে গঠিত হয় ‘ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব’। ঢাকার ওয়ারী ক্লাব থেকে এ সময় দীনেশ গুহ, ভোলা, ভানু দত্ত রায়, প্রশান্ত, পোদ্দার- প্রমুখ ফুটবলার ইস্ট বেঙ্গলে যোগ দেন।
সে স ম য়ে র ক’ জ ন সে রা
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) দিন বদলের সাথে ফুটবলে ঢাকার ছেলেদের নৈপুণ্য বাড়তে থাকে আর বাড়তে থাকে তাদের চাহিদা। আজ ইউরোপীয় ক্লাবগুলো যেমন ঝুঁকে পড়েছে আফ্রিকার ফুটবলারদের দিকে, তেমনি দশ এবং বিশের দশকে কলকাতার ক্লাবগুলো ঢাকার ফুটবলারদের দলে ভেড়ানোর জন্য যেনো উন্মুখ হয়ে থাকতো। এবার তেমনি চাহিদা সম্পন্ন ঢাকার ক’জন ফুটবলারের ওপর আলোকপাত করা যাক- তাঁর প্রকৃত নাম ছিলো যতীন্দ্রনাথ রায়। তবে ফুটবল জগতে কানু রায় নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ঢাকার ওয়ারী ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড়। কানু রায় ছিলেন সেকালের সর্বজনস্বীকৃত সেরা রাইট আউট। যদিও তিনি সমান দক্ষতায় লেফটআউট পজিশনেও খেলতে পারতেন। পরে তিনি মোহনবাগানে যোগ দেন।
দিন বদলের সাথে ফুটবলে ঢাকার ছেলেদের নৈপুণ্য বাড়তে থাকে আর বাড়তে থাকে তাদের চাহিদা। আজ ইউরোপীয় ক্লাবগুলো যেমন ঝুঁকে পড়েছে আফ্রিকার ফুটবলারদের দিকে, তেমনি দশ এবং বিশের দশকে কলকাতার ক্লাবগুলো ঢাকার ফুটবলারদের দলে ভেড়ানোর জন্য যেনো উন্মুখ হয়ে থাকতো। এবার তেমনি চাহিদা সম্পন্ন ঢাকার ক’জন ফুটবলারের ওপর আলোকপাত করা যাক- তাঁর প্রকৃত নাম ছিলো যতীন্দ্রনাথ রায়। তবে ফুটবল জগতে কানু রায় নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ঢাকার ওয়ারী ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড়। কানু রায় ছিলেন সেকালের সর্বজনস্বীকৃত সেরা রাইট আউট। যদিও তিনি সমান দক্ষতায় লেফটআউট পজিশনেও খেলতে পারতেন। পরে তিনি মোহনবাগানে যোগ দেন।
ঢাকার আর এক খেলোয়াড় রাজেন সেনগুপ্ত। অসামান্য ফুটবল দক্ষতার কারণে তার নাম ছিলো সকলের মুখে মুখে। তাকে অনেকেই ইতিহাস সৃষ্টিকারী ফুটবলারও বলে থাকেন। তিনি হাফ সেন্টার পজিশনে খেলতেন। রাজেন সেনগুপ্ত ওয়ারীতে খেলতেন, পরে যোগ দেন মোহনবাগানে।
ঢাকার আর এক বিখ্যাত খেলোয়াড় হচ্ছেন নগেন কালী। মোহনবাগানের হয়ে খেলে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন।
কলকাতার ফুটবলে একসময় বাঘা সোম নামটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। বাঘা সোমের প্রকৃত নাম ছিলো তেজশচন্দ্র সোম। তিনি ইনসাইট পজিশনে খেলা শুরু করলেও পরে হাফসেন্টার পজিশনে খেলে প্রশংসা কুড়ান। এ ছাড়া মেজর জেনারেল এবিএস রায়, সিদ্দিক দেওয়ান, সোনা মিয়া, সাহেব আলী, আলাউদ্দিন, রশিদ, আব্বাস মির্জা, মোনা দত্ত প্রমুখ খেলোয়াড়রা নিজ ফুটবল গুণে আলোচনায় ঠাঁই করে নেন।
ঢা কা র ফু ট ব ল
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) সেকালের ফুটবলের সোনালী তারকা শেখ মোহাম্মদ সাহেব আলীর নাম কারো অজানা নয়। পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এক স্মৃতিচারণে পাওয়া যায়- ১৯৩১ সালের দিকে ঢাকায় খেলার জন্য নির্দিষ্ট ছিলো পল্টন ময়দান। বর্তমান ঢাকা স্টেডিয়ামের উত্তর গেটের স্থানে ছিলো পুলিশের চানমায়ী পাহাড় এবং পাহাড় লাগোয়া দক্ষিণ দিকে ছিলো জঙ্গল। বর্তমান বঙ্গভবনের স্থানে ছিলো একটা সুদৃশ্য বাগানবাড়ি। এ বাড়িতে বাস করতেন তৎকালীন সামরিক বাহিনীর এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। পল্টন ময়দানে ছিলো ওয়ারী, ভিক্টোরিয়া ও লক্ষীবাজার ক্লাব। ক্লাবের নিজ নিজ মাঠ ছিলো টিন দিয়ে ঘেরা। বর্তমান ভলিবল মাঠটি ছিলো ঈদগাহ ময়দান। অবশ্য এটা মাদ্রাসা ও মুসলিম হাই স্কুলের ছাত্রদের খেলার মাঠ হিশেবেও ব্যবহার হতো। বর্তমান জেনারেল পোস্ট অফিসের স্থানে ছিলো জগন্নাথ কলেজের খেলার মাঠ। এ মাঠে আন্তঃস্কুল ও আন্তঃকলেজ ফুটবল অনুষ্ঠিত হতো।
সেকালের ফুটবলের সোনালী তারকা শেখ মোহাম্মদ সাহেব আলীর নাম কারো অজানা নয়। পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এক স্মৃতিচারণে পাওয়া যায়- ১৯৩১ সালের দিকে ঢাকায় খেলার জন্য নির্দিষ্ট ছিলো পল্টন ময়দান। বর্তমান ঢাকা স্টেডিয়ামের উত্তর গেটের স্থানে ছিলো পুলিশের চানমায়ী পাহাড় এবং পাহাড় লাগোয়া দক্ষিণ দিকে ছিলো জঙ্গল। বর্তমান বঙ্গভবনের স্থানে ছিলো একটা সুদৃশ্য বাগানবাড়ি। এ বাড়িতে বাস করতেন তৎকালীন সামরিক বাহিনীর এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। পল্টন ময়দানে ছিলো ওয়ারী, ভিক্টোরিয়া ও লক্ষীবাজার ক্লাব। ক্লাবের নিজ নিজ মাঠ ছিলো টিন দিয়ে ঘেরা। বর্তমান ভলিবল মাঠটি ছিলো ঈদগাহ ময়দান। অবশ্য এটা মাদ্রাসা ও মুসলিম হাই স্কুলের ছাত্রদের খেলার মাঠ হিশেবেও ব্যবহার হতো। বর্তমান জেনারেল পোস্ট অফিসের স্থানে ছিলো জগন্নাথ কলেজের খেলার মাঠ। এ মাঠে আন্তঃস্কুল ও আন্তঃকলেজ ফুটবল অনুষ্ঠিত হতো।
ডি এস এ গ ঠ ন
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) দেশের খেলাধুলার সার্বিক উন্নতি ও পৃষ্ঠপোষকতা দানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৩৩ সালে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এক সভায় মিলিত হন। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন খান বাহাদুর খাজা মোহাম্মদ ইসমাইল, জমিদার রায় বাহাদুর, পি গুপ্ত, কেশব চন্দ্র ব্যানার্জি, জমিদার সুরেশ চন্দ্র ধাম, বারোদার জমিদার পুত্র নৃপেন্দ্র রায় চৌধুরী, খাজা মোহাম্মদ আদেল, এনপি গুপ্ত, খাজা মোহাম্মদ আজমল, এপি গুপ্ত প্রমুখ। সভায় উপস্থিত সকলে একমত হয়ে গঠন করেন ‘ ঢাকা স্পোর্টিং এসোসিয়েশন’ অর্থাৎ ‘ডিএসএ’। ঢাকার বিভাগীয় কমিশনারকে সভাপতি ও পি গুপ্তকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত হয় ডিএসএ’র প্রথম কার্যকরী কমিটি।
দেশের খেলাধুলার সার্বিক উন্নতি ও পৃষ্ঠপোষকতা দানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৩৩ সালে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এক সভায় মিলিত হন। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন খান বাহাদুর খাজা মোহাম্মদ ইসমাইল, জমিদার রায় বাহাদুর, পি গুপ্ত, কেশব চন্দ্র ব্যানার্জি, জমিদার সুরেশ চন্দ্র ধাম, বারোদার জমিদার পুত্র নৃপেন্দ্র রায় চৌধুরী, খাজা মোহাম্মদ আদেল, এনপি গুপ্ত, খাজা মোহাম্মদ আজমল, এপি গুপ্ত প্রমুখ। সভায় উপস্থিত সকলে একমত হয়ে গঠন করেন ‘ ঢাকা স্পোর্টিং এসোসিয়েশন’ অর্থাৎ ‘ডিএসএ’। ঢাকার বিভাগীয় কমিশনারকে সভাপতি ও পি গুপ্তকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত হয় ডিএসএ’র প্রথম কার্যকরী কমিটি।
ঢাকার ফুটবলের উন্নয়নে ডিএসএ’র প্রচেষ্টা ছিলো লক্ষ্যণীয়। প্রাথমিক দিকে এসোসিয়েশনের কোনো মাঠ কিংবা অফিস ছিলো না। ওয়ারী ক্লাবের একটি কক্ষ তারা অফিস হিসেবে ব্যাবহার করতো। তাদের আয়োজনে ফুটবল লীগ ও নকআউট টুর্নামেন্টগুলো অনুষ্ঠিত হতো লক্ষীবাজার, ভিক্টোরিয়া, ওয়ারী ও জগন্নাথ কলেজ মাঠে। সে সময় বাঁশের বেড়া দ্বারা ঘিরে টিকিট দিয়ে খেলা অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৩৬ সালে তৈরী হয় টিনের চাল, টিনের বেড়া ও কাঠের ফ্লোরের ডিএসএ প্যাভিলিয়ন । আর এ বছর ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় বিভাগের দল ইজলিন্টন করিনথিয়ন ঢাকা সফরে এলে এ নতুন মাঠেই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম খেলায় সফরকারী দলের বিরুদ্ধে ঢাকা একাদশ ০-১ গোলে জয়লাভ করে। দলের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন পাখি সেন। ইজলিন্টন করিনথিয়নের বিরুদ্ধে ঢাকা একাদশ পরে আরো একটি খেলায অংশগ্রহণ করে। এ সম্পর্কে সাবেক ফুটবলার সাহেব আলী তার এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ‘খেলা দুটোতে টিকিটের হার ছিলো- মাটিতে এক টাকা, কাঠের গ্যলারী দুই টাকা এবং চেয়ার পাঁচ টাকা। এ দুই খেলায় ২০ হাজার টাকারও বেশী টিকিট বিক্রি হয়। আর এ টিকিট বিক্রির পরিমাণ দেখে বোঝা যায়, সে সময় ঢাকায় ফুটবল কতোটা জনপ্রিয় ছিলো। যখন ঢাকায় লোকসংখ্যা আর বসতি ছিলো কম, তখনই যদি বিশ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়ে থাকে তবে খুব সহজেই অনুমেয়, গোড়া থেকে ঢাকাবাসী ফুটবলকে তাদের হৃদয়ে কতোটা ধারণ করতো। অথচ দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, আজ এমনও খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে যেখানে দু’হাজার টাকারও টিকিট বিক্রি হয় না। ডিএসএ’র আয়োজনে সে সময় ঢাকায় কলকাতার ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মুসলিম একাদশ, মোহামেডানের মতো বিখ্যাত ক্লাবগুলো ছাড়াও বিলেতের অনেক দল খেলতে আসতো। আর এসব খেলায় বিপুল দর্শক সমাগম ঘটতো। প্রাক্তন ফুটবলার সাহেব আলী তার আর এক নিবন্ধের এক স্থানে বলেছেন, ‘প্রদর্শনী খেলাগুলোতে একমাত্র কলকাতা মোহামেডানই প্রতিবার বিজয়ী হয়েছে।’ অর্থাৎ অন্যান্য দল ঢাকার দলগুলোর কাছে হেরে যেতো। এ থেকে বোঝা যায়, সে সময় ঢাকার ফুটবলের শক্তিমত্তা। আর ‘ঢাকা একাদশ’ তো ছিলো অধিক শক্তিশালী। সাহেব আলী তার নিবন্ধে আরো লিখেছেন, ‘চল্লিশের দশকে ঢাকায় খেলতে আসা বিদেশী বা ভারতবর্ষের কোনো দলের মধ্যে একমাত্র কলকাতা মোহামেডানই একবার ঢাকা একাদশকে হারাতে পেরেছিলো’। ১৯৩২ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত ঢাকার ফুটবল লীগে যেসব ক্লাব অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ওয়ারী ক্লাব, ভিক্টোরিয়া এসসি, লক্ষিবাজার ক্লাব, ইস্ট এন্ড ক্লাব, সেন্ট্রাল জেল একাদশ, আরমানী টোলা ক্লাব, রমনা এসি, ঢাকা মুসলিম ওয়ান্ডারার্স (পরে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স), মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, তেজগাঁও ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, ঢাকেশ্বরী কটন মিলস, মনিপুর ফার্ম, বিজিএইচ। এছাড়া জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ, সলিমুল্লাহ কলেজ, ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজ, ঢাকা হল, জগন্নাথ হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, এআরপি (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সিভিল ডিফেন্স, ফাস্ট এইড ও ফায়ার সার্ভিস কার্যক্রম পরিচালিত প্রতিষ্ঠান) ও ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস (গুর্খা রেজিমেন্ট) দলগুলো রোনাল্ড শিল্ডসহ বিভিন্ন নকআউট ফুটবলে অংশগ্রহণ করতো। এ সময় প্রতি বছর লীগের পাশাপাশি রোনাল্ড শিল্ড নকআউট ফুটবল অনুষ্ঠিত হতো। ত্রিশের দশকে ঢাকার জনপ্রিয় দলগুলোর মধ্যে সেরা ছিলো ওয়ারী, ভিক্টোরিয়া ও মনিপুর ফার্ম।
ঢা কা র শি ক্ষা ঙ্গ নে ফু ট ব ল
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) সে সময় ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে খেলাধুলার চর্চা ছিলো বেশ। শিক্ষার পাশাপাশি ক্রীড়াকে গুরুত্ব দিতেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। তারা বেশ বুঝতেন যে, সুস্থ দেহ আর সুন্দর মন না হলে বিদ্যা চর্চা চলে না। আর সুস্থদেহ ও সুন্দর মন গড়ার প্রধান শর্তই হচ্ছে খেলাধুলা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাই বলে গেছেন, ‘চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, চাই উজ্জ্বল পরমায়ু।’ আর এজন্য প্রয়োজন খেলাধুলা। আজ ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা নানা ধাঁচের, নানা আকৃতি-প্রকৃতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢাকা সয়লাব। আর এসব প্রতিষ্ঠানে নানা কায়দায় ছাত্রদের বেটে খাওয়ানো হচ্ছে বিদ্যা। শিক্ষকরা গলদঘর্ম তাদের বুদ্ধি বাড়ানোর প্রক্রিয়ায়। কিন্তু তাতে কি ভবিষ্যতের সুন্দর, সুস্থ জাতির নিশ্চয়তা মিলছে? আজকের এই সব শিক্ষালয়ে ছাত্রদের খেলাধুলার বিষয়টি উপেক্ষিত হলেও অতীতে এমনটি ছিলোনা। খুব বেশী পেছনে নাই বা গেলাম। স্বাধীনতার পরও সত্তরের দশকে স্কুল-কলেজগুলোতে খেলাধুলার যে চিত্র চোখে পড়তো আজ কি তা আছে? ফুটবল ছাড়া ছেলেদের স্কুল-কলেজ তো কল্পনাই করা যেতো না।
সে সময় ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে খেলাধুলার চর্চা ছিলো বেশ। শিক্ষার পাশাপাশি ক্রীড়াকে গুরুত্ব দিতেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। তারা বেশ বুঝতেন যে, সুস্থ দেহ আর সুন্দর মন না হলে বিদ্যা চর্চা চলে না। আর সুস্থদেহ ও সুন্দর মন গড়ার প্রধান শর্তই হচ্ছে খেলাধুলা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাই বলে গেছেন, ‘চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, চাই উজ্জ্বল পরমায়ু।’ আর এজন্য প্রয়োজন খেলাধুলা। আজ ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা নানা ধাঁচের, নানা আকৃতি-প্রকৃতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢাকা সয়লাব। আর এসব প্রতিষ্ঠানে নানা কায়দায় ছাত্রদের বেটে খাওয়ানো হচ্ছে বিদ্যা। শিক্ষকরা গলদঘর্ম তাদের বুদ্ধি বাড়ানোর প্রক্রিয়ায়। কিন্তু তাতে কি ভবিষ্যতের সুন্দর, সুস্থ জাতির নিশ্চয়তা মিলছে? আজকের এই সব শিক্ষালয়ে ছাত্রদের খেলাধুলার বিষয়টি উপেক্ষিত হলেও অতীতে এমনটি ছিলোনা। খুব বেশী পেছনে নাই বা গেলাম। স্বাধীনতার পরও সত্তরের দশকে স্কুল-কলেজগুলোতে খেলাধুলার যে চিত্র চোখে পড়তো আজ কি তা আছে? ফুটবল ছাড়া ছেলেদের স্কুল-কলেজ তো কল্পনাই করা যেতো না।
ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ফুটবল ছিলো বেশ সরব। লীগ ও নকআউট ফুটবল ছাড়াও নিয়মিতভাবে আন্তঃকলেজ ও আন্তঃহল ফুটবল জমজমাটভাবেই অনুষ্ঠিত হতো। এ সব প্রতিযোগিতায় স্বাগতিক ঢাকা জেলার কলেজ দল ছাড়াও অন্যান্য জেলা অংশ নিতো। ভারতের প্রেসিডেন্সি কলেজ ও রিপন কলেজের ফুটবল দল প্রতি বছরই ঢাকার বিভিন্ন কলেজ দল বা হল দলের সাথে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে আসতো। প্রতি বছর ‘ঢাকা সিটি আন্তঃস্কুল’ ফুটবল অনুষ্ঠিত হতো। দিনে দিনে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলার স্কুলগুলোতে ফুটবলের প্রসার ঘটতে থাকে। এর সাথে বাড়তে থাকে প্রতিযোগিতা।
জে লা প র্যা য়ে ফু ট ব ল
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) সে সময় জেলা পর্যায়েও ফুটবল ছিলো জমজমাট। ময়মনসিংহের ‘সূর্যকান্ত শিল্ড’ রংপুরের ‘গোবিন্দলাল শিল্ড’, দিনাজপুরের নরনারায়ণ রামকানাই কুন্ড শিল্ড’-এর প্রতিযোগিতা ছিলো দেশ-বিদেশে আলোচিত। এসব প্রতিযোগিতায় ঢাকা ছাড়াও কলকাতা প্রথম বিভাগের নামী-দামী দল অংশ নিতো। অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে শিরোপার জন্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতো। ঢাকা ও কলকাতার বিখ্যাত অনেক ফুটবলার এসব প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বাড়াতেন। স্বীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করে দর্শকদের নয়ন ও মন ভরাতেন, এবং প্রভাবিত করতেন স্থানীয় তারুণ্যকে। এদের সংস্পর্শে রঙিন স্বপ্ন ছড়িয়ে পড়তো স্থানীয় উঠতি ফুটবলারদের চোখে। জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এসব প্রতিযোগিতার ফলে যেমন বাড়তো দর্শক, তেমন ঘটতো ফুটবলের প্রসার।
সে সময় জেলা পর্যায়েও ফুটবল ছিলো জমজমাট। ময়মনসিংহের ‘সূর্যকান্ত শিল্ড’ রংপুরের ‘গোবিন্দলাল শিল্ড’, দিনাজপুরের নরনারায়ণ রামকানাই কুন্ড শিল্ড’-এর প্রতিযোগিতা ছিলো দেশ-বিদেশে আলোচিত। এসব প্রতিযোগিতায় ঢাকা ছাড়াও কলকাতা প্রথম বিভাগের নামী-দামী দল অংশ নিতো। অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে শিরোপার জন্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতো। ঢাকা ও কলকাতার বিখ্যাত অনেক ফুটবলার এসব প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বাড়াতেন। স্বীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করে দর্শকদের নয়ন ও মন ভরাতেন, এবং প্রভাবিত করতেন স্থানীয় তারুণ্যকে। এদের সংস্পর্শে রঙিন স্বপ্ন ছড়িয়ে পড়তো স্থানীয় উঠতি ফুটবলারদের চোখে। জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এসব প্রতিযোগিতার ফলে যেমন বাড়তো দর্শক, তেমন ঘটতো ফুটবলের প্রসার।
আ ন্তঃ প্রা দে শি ক ফু ট ব লে ঢা কা
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) ১৯৪০ সালের ১৫ এপ্রিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের চতুর্থ সাধারণ বার্ষিক সভায় ঢাকা স্পোর্টিং এসেসিয়েশনের সভাপতি পঙ্কজ গুপ্ত আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল চালু করার প্রস্তাব দিলে তা অনুমোদিত হয় এবং মান বিবেচনা করে ঢাকাকে আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল খেলার ব্যাপারে প্রভিনশিয়াল মর্যাদা দেয়া হয়। কিন্তু সে বছর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে ঢাকা ডিএসএ সে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেনি। ১৯৪৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল। এ প্রতিযোগিতায় ডিএসএ পশ্চিমবঙ্গ একাদশের কাছে ০-২ গোলে পরাজিত হয়। ডিএসএ’র পক্ষে খেলেন- কমলেন্দু সেন, চিনু ঘোষ, সাহেব আলী, সুবোধ মিত্র, রতিশ তালুকদার, যোগেস রায়, অনিল ধর, খোকা ধর, অনিল ররুদ্র, সার্জেন্ট ডিমেলো ও সার্জেন্ট জোন্স। এছাড়া ১৯৪৫ সালে বোম্বে কুপারেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় ফুটবলে ডিএসএ দল ১-৩ গোলে বোম্বে প্রদেশের কাছে পরাজিত হয়। এ খেলায় নিয়মভঙ্গ করে চারজন বৃটিশ খেলোয়াড় বোম্বের পক্ষে খেলেন। বৃটিশ শাসনামলে এদেশের শিক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই ছিলো হিন্দুদের আধিপত্য। মুসলিম সমাজ ছিলো অবহেলিত ও উপক্ষেতি। ১৯৪৩ সালে ঢাকায় এবং ১৯৪৫ সালে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ডিএসএ’র পক্ষে একমাত্র মুসলিম খেলোয়াড় হিসেবে খেলার সুযোগ পান সাহেব আলী।
১৯৪০ সালের ১৫ এপ্রিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের চতুর্থ সাধারণ বার্ষিক সভায় ঢাকা স্পোর্টিং এসেসিয়েশনের সভাপতি পঙ্কজ গুপ্ত আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল চালু করার প্রস্তাব দিলে তা অনুমোদিত হয় এবং মান বিবেচনা করে ঢাকাকে আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল খেলার ব্যাপারে প্রভিনশিয়াল মর্যাদা দেয়া হয়। কিন্তু সে বছর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে ঢাকা ডিএসএ সে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেনি। ১৯৪৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল। এ প্রতিযোগিতায় ডিএসএ পশ্চিমবঙ্গ একাদশের কাছে ০-২ গোলে পরাজিত হয়। ডিএসএ’র পক্ষে খেলেন- কমলেন্দু সেন, চিনু ঘোষ, সাহেব আলী, সুবোধ মিত্র, রতিশ তালুকদার, যোগেস রায়, অনিল ধর, খোকা ধর, অনিল ররুদ্র, সার্জেন্ট ডিমেলো ও সার্জেন্ট জোন্স। এছাড়া ১৯৪৫ সালে বোম্বে কুপারেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় ফুটবলে ডিএসএ দল ১-৩ গোলে বোম্বে প্রদেশের কাছে পরাজিত হয়। এ খেলায় নিয়মভঙ্গ করে চারজন বৃটিশ খেলোয়াড় বোম্বের পক্ষে খেলেন। বৃটিশ শাসনামলে এদেশের শিক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই ছিলো হিন্দুদের আধিপত্য। মুসলিম সমাজ ছিলো অবহেলিত ও উপক্ষেতি। ১৯৪৩ সালে ঢাকায় এবং ১৯৪৫ সালে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ডিএসএ’র পক্ষে একমাত্র মুসলিম খেলোয়াড় হিসেবে খেলার সুযোগ পান সাহেব আলী।
যা দু ক র সা মা দ
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) ভারতীয় উপমহাদেশে ফুটবলের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অধ্যায়টি যিনি রচনা করেছেন তিনি হচ্ছেন যাদুকর সামাদ। দেশ-বিদেশে কেনা শুনেছে তার নাম? এক সামাদ তাঁর ফুটবল নৈপুণ্য দিয়ে বিশ্বের দরবারে ভারতবাসীকে যেভাবে তুলে ধরেছিলেন তা এক অনন্য ইতিহাস। ফুটবল যেনো তাঁর কথা শুনতো, ফুটবলের সাথে তাঁর সম্পর্কটা ছিলো নিখুঁত। আর তাই সামাদের নামের পেছনে জুড়ে আছে ‘ফুটবলের কিংবদন্তীর মহান নায়ক’, ‘ইতিহাস সৃষ্টিকারী ফুটবলার’ ইত্যাদি নানা বিশেষণ। সময়টা ত্রিশের দশক। বাঙালী জাতি তখন শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হারানো অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সোচ্চার। এ সময় ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গনে যে সকল ক্রীড়াবিদ দেশে-বিদেশে নিজস্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছেন এক কথায় সামাদ তাদের মধ্যে প্রধান। সামাদ তাঁর খেলোয়াড়ী জীবনে ফুটবলের সবুজ চত্বরে নিজের অসাধারণ নৈপুণ্যের অপরূপ কারুকাজে এমন সব ঘটনার জন্ম দিয়েছিলেন, যা ফুটবল ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আর তার এই ব্যতিক্রমধর্মী অসাধারণ যাদুকরী ফুটবল নৈপুণ্যের কারণে তিনি ভূষিত হয়েছিলেন ‘ফুটবল যাদুকর’ উপাধিতে।
ভারতীয় উপমহাদেশে ফুটবলের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অধ্যায়টি যিনি রচনা করেছেন তিনি হচ্ছেন যাদুকর সামাদ। দেশ-বিদেশে কেনা শুনেছে তার নাম? এক সামাদ তাঁর ফুটবল নৈপুণ্য দিয়ে বিশ্বের দরবারে ভারতবাসীকে যেভাবে তুলে ধরেছিলেন তা এক অনন্য ইতিহাস। ফুটবল যেনো তাঁর কথা শুনতো, ফুটবলের সাথে তাঁর সম্পর্কটা ছিলো নিখুঁত। আর তাই সামাদের নামের পেছনে জুড়ে আছে ‘ফুটবলের কিংবদন্তীর মহান নায়ক’, ‘ইতিহাস সৃষ্টিকারী ফুটবলার’ ইত্যাদি নানা বিশেষণ। সময়টা ত্রিশের দশক। বাঙালী জাতি তখন শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হারানো অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সোচ্চার। এ সময় ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গনে যে সকল ক্রীড়াবিদ দেশে-বিদেশে নিজস্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছেন এক কথায় সামাদ তাদের মধ্যে প্রধান। সামাদ তাঁর খেলোয়াড়ী জীবনে ফুটবলের সবুজ চত্বরে নিজের অসাধারণ নৈপুণ্যের অপরূপ কারুকাজে এমন সব ঘটনার জন্ম দিয়েছিলেন, যা ফুটবল ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আর তার এই ব্যতিক্রমধর্মী অসাধারণ যাদুকরী ফুটবল নৈপুণ্যের কারণে তিনি ভূষিত হয়েছিলেন ‘ফুটবল যাদুকর’ উপাধিতে।
প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, মাত্র ১২ বছর বয়সে সামাদ শুরু করেন তাঁর বিস্ময়কর ফুটবল জীবন। ১৯১২ সালে প্রথম কলকাতা মেইন টাউন ক্লাবের পক্ষে খেলেন। ১৯১৮ সালে এরিয়েন্স ক্লাবের সদস্য হন। ১৯১৯ সালে তাজহাট ক্লাবের পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯২১ সাল থেকে ’৩১ সাল পর্যন্ত খেলেন ইবিআর দলে। ভারতের জাতীয় দলের হয়ে তিনি ইন্দোনেশিয়ার জাভায় খেলতে যান ১৯২৪ সালে। উল্লেখ্য, এটাই ছিলো ভারতীয় দলের প্রথম বিদেশ সফর। এরপর তিনি পুনরায় জাভায় যান ১৯২৬ সালে। একই বছর সামাদের নৈপুণ্যের ওপর ভর করে কলকাতা মোহামেডান জয় করে ‘ডুরান্ড কাপ’। সামাদ ১৯৩২ সালে অল ইন্ডিয়া দলের হয়ে খেলতে যান শ্রীলঙ্কায়। ১৯৩৩ সালে যোগ দেন কলকাতা মোহামেডানে। ঐ বছরই উন্নত মানের খেলা উপহার দেয়ার জন্য তাঁকে ‘হিরো অব দ্য গেমস’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। পরবর্তী বছরগুলো ছিলো মোহামেডানের স্বর্ণযুগ। আর মোহামেডানের এই স্বর্ণযুগের রচয়িতা ছিলেন সামাদ। সামাদের অসাধারণ যাদুকরী নৈপুণ্যের কারণেই মোহামেডান পর পর পাঁচবার আইএফএ শিল্ড জয় ও লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সাতচল্লিশে দেশ বিভাগের পর সামাদ স্বপরিবারে এ দেশে চলে আসেন এবং পার্বতীপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। চাকুরী পান রেল জংশনে প্লাটফরম ইন্সপেক্টর হিসেবে। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এ চাকুরী করে অবসর নেন। এবং এর ৭ বছর পর ১৯৬৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
সামাদ যে কতো বড় ফুটবল যাদুকর ছিলেন, তা গোটা তিনেক ঘটনা থেকেই সহজে অনুমেয়। সামাদের মেয়ে জামিলা খাতুনের মুখে শোনা যায় তার পিতার এসব ফুটবল কেরামতির কথা –
১. একবার তিনি এক মাঠে খেলতে গিয়ে মাঠের চারিদিকে ঘুরে ফিরে পায়চারী করে বললেন, মাঠটি আন্তর্জাতিক মাপের চাইতে ছোট আছে। সুতরাং তিনি এ মাঠে খেলবেন না। পরে মাঠ মাপার পর তার বক্তব্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়।
২. ইন্দোনেশিয়ার জাভায় দ্বিতীয়বার খেলতে গিয়ে খেলা চলাকালে তিনি গোলবারে একটি শট নিলেন। বল বারে লেগে চলে গেলো মাঠের বাইরে। সামাদ চ্যালেঞ্জ করে বললেন, ‘নিশ্চয় গোলপোস্ট ছোট আছে। আমার শট মানেই নিখুঁত মাপা শট। তা মিস হবার কথা নয়।’ পরে গোলবার মেপে দেখা গেলো, সমাদ ঠিকই বলেছেন, গোলবারটি নির্ধারিত মাপের চাইতে ছোট। এমন চ্যালেঞ্জ কি আজকের দিনেও কোনো খেলোয়াড়ের পক্ষে রাখা সম্ভব?
৩. দায়ভাঙ্গার রানী তো সামাদের নাম শুনে শুনে অস্থির। একবার তিনি রাজাকে বললেন, ‘আমার বড্ড ইচ্ছে করছে সামাদের খেলা দেখতে।’ রাজার নিজেরও যে ইচ্ছে ছিলো না তা নয়। রাজা বিহারের সব নামী-দামী ফুটবলারদের একত্রিত করে ‘বিহার একাদশ’ গঠন করলেন এবং এই দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন সামাদের দল কলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে। সামাদ তখন মোহামেডানে খেলতেন। রাজা ও রানীর সঙ্গে হাজার হাজার দর্শক উদগ্রীব হয়ে আছে সামাদের খেলা দেখার জন্য। শুরু হলো খেলা। তুমুল উত্তেজনা। দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বীতা। অথচ সামাদ তখন পর্যন্ত মোটেও খেলছেন না। মাঝে মাঝে মাঠে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিচ্ছেন। যার খেলা দেখার জন্য এতো আয়োজন, এই কি না তার খেলার নমুনা! রানী বিরক্ত হয়ে মোহামেডানের কর্মকর্তা নুরুদ্দিনকে ডেকে বললেন- ‘এই বুঝি তোমাদের সামাদ, যে কিনা একজন সাধারণ খেলোয়াড়ের চাইতেও খারাপ খেলছে!’ বিরতির সময় কথাটা সামাদের কানে গেলো। তিনি রানীর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন- ‘মহারানী ছাহেবা, আপ কেতনে গোল চাহতি হ্যায়?’ উত্তরে রানী বললেন- ‘তিনটি’। সামাদ বললেন- ‘ঠিক হ্যায়।’ বিরতির পর খেলা আবার শুরু হলো। সামাদ মুচকি হেসে মাঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গোঁফে তা দিলেন। এর কিছু পরই তিনি শুরু করলেন তার পায়ে-বলে আগুন ঝরানো খেলা। আর অতি অল্প সময়ে বিস্ময়কর দক্ষতায় পর পর তিনটি গোল করলেন। খেলা শেষে আবেগাপ্লুত রানী নিজের গলার মূল্যবান হার খুলে সামাদের গলায় পরিয়ে দিলেন। উপমহাদেশের এই ফুটবল যাদুকরের ফুটবল জীবন মানেই আমাদের ফুটবলের সোনালী অধ্যায়। সামাদ আমাদের গর্ব, অহঙ্কার। তবে ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে, এর পর থেকে আজও এখানে সামাদের মতো আর কোনো বিস্ময়কর ফুটবল প্রতিভার জন্ম হয়নি। আর সামাদের দুর্ভাগ্য যে, কখনোই তার প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি।
দে শ ভা গে র প র
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তের পর ঢাকার ক্রীড়াঙ্গনে একটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ক্লাবের হিন্দু পৃষ্টপোষক ও সংগঠকরা দেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেলে একটা স্থবিরতা যেনো জেঁকে বসে ঢাকার ফুটবলেও। কিন্তু এ সময়টা খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় না। ’৪৭-এ দেশ ভাগের পর পূর্বে বাংলা এবং পশ্চিমে পাঞ্জাব-সিন্ধু-বেলুচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নিয়ে সূচিত হয় নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান। মূলত ধর্মের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারিত হয়। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এবং পরবর্তীতে রাজনৈতিক অস্থিরতা যে এদেশের খেলাধুলার ওপর প্রভাব ফেলেনি তা নয়, কিন্তু তারপরও ক্রীড়াক্ষেত্রের গতি ছিলো সচল। তবে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) মানুষ বেশ উপলব্ধি করলো, এই দেশ বিভাগে আসলে তাদের লাভ কিছুই হয়নি, শুধু প্রভুর পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। ইংরেজদের আসনে বসেছে করাচি-লাহোরের অবাঙ্গালী প্রভু। আর এই অবাঙ্গালী প্রভুরা ক্রীড়াক্ষেত্রেও তাদের প্রভুত্ব বিস্তারে ছিলো সোচ্চার। ফলে পাক আমলে এদেশের ক্রীড়াবিদরা বিভিন্ন সময়ে বৈষম্যের শিকার হয়েছে। বঞ্চিত হয়েছে নানা সুযোগ থেকে। জাতীয় দল গঠনে থেকেছে উপেক্ষিত। তারপরও এদেশের ফুটবল থেমে থাকেনি। ৫২’র ভাষা আন্দোলনের বছরও ঢাকায় ফুটবল লীগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বছর বিজি প্রেস লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং ওয়ান্ডারার্স রানার্সআপ হয়। তবে বরেণ্য প্রবীন ক্রীড়া সাংবাদিক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান তার এক নিবন্ধে লিখেছেন- ‘পঞ্চাশের দশকে ফুটবলে প্রান ছিলো না। আর এই প্রানহীন, গতিহীন ফুটবলে সে সময়ের কিছু ফুটবলার প্রান ও গতি ফিরিয়ে এনেছিলেন।’ কামরুজ্জামান যাদের মধ্যে দাউদকান্দির ছেলে আশরাফ চৌধুরীকে অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, পঞ্চাশের দশকে ইপিআর-এর শওকত, ক্যাপ্টেন নেওয়াজ, বিজি প্রেসের ছুন্না রশিদ, আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের আনোয়ার, মান্না, ওয়ান্ডারার্সের বলাই, বাহারাম, মহারাজ, সেন্ট্রাল স্টেশনারীর চার্লস, জামাল, ওয়ারীর আউয়াল প্রমুখ খেলোয়াড়রদের নৈপুণ্য সে সময়ের দর্শকদের নজর কাড়ে। এ সময়টাতে আরো যারা নিজেদের ফুটবল নৈপুন্য দিয়ে এদেশের ফুটবলকে আলোকিত করেছিলেন, তাদের মধ্যে মিয়াজী, মোমতাজ, রঞ্জিত, নবী চৌধুরী, ভাওয়াল ওয়াজেদ, সাদেক, মঞ্জুর হাসান মিন্টু, কামরুজ্জামান, সিতাংশু প্রমূখের নাম উল্লেখযোগ্য। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আরো যে সব খেলোয়াড় স্বীয় নৈপুণ্য দ্বারা ফুটবলকে আলোকিত করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, গজনবী, আরজু, কবির, আশ্রাফ, শাহ আলম, আমান, পি ঘোষ, সামাদ, হুমায়ুন, নাসির, তফাজ্জল, কানু, মারি, খায়ের, নজরুল, মদন, দেবাশীষ, আবেদ, কালা গফুর, রাহি, সিদ্দিক, আম্বিয়া, হাশেম দীন, কাদিও, কাইয়ুম, চেঙ্গেজি প্রমূখ।
১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তের পর ঢাকার ক্রীড়াঙ্গনে একটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ক্লাবের হিন্দু পৃষ্টপোষক ও সংগঠকরা দেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেলে একটা স্থবিরতা যেনো জেঁকে বসে ঢাকার ফুটবলেও। কিন্তু এ সময়টা খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় না। ’৪৭-এ দেশ ভাগের পর পূর্বে বাংলা এবং পশ্চিমে পাঞ্জাব-সিন্ধু-বেলুচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নিয়ে সূচিত হয় নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান। মূলত ধর্মের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারিত হয়। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এবং পরবর্তীতে রাজনৈতিক অস্থিরতা যে এদেশের খেলাধুলার ওপর প্রভাব ফেলেনি তা নয়, কিন্তু তারপরও ক্রীড়াক্ষেত্রের গতি ছিলো সচল। তবে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) মানুষ বেশ উপলব্ধি করলো, এই দেশ বিভাগে আসলে তাদের লাভ কিছুই হয়নি, শুধু প্রভুর পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। ইংরেজদের আসনে বসেছে করাচি-লাহোরের অবাঙ্গালী প্রভু। আর এই অবাঙ্গালী প্রভুরা ক্রীড়াক্ষেত্রেও তাদের প্রভুত্ব বিস্তারে ছিলো সোচ্চার। ফলে পাক আমলে এদেশের ক্রীড়াবিদরা বিভিন্ন সময়ে বৈষম্যের শিকার হয়েছে। বঞ্চিত হয়েছে নানা সুযোগ থেকে। জাতীয় দল গঠনে থেকেছে উপেক্ষিত। তারপরও এদেশের ফুটবল থেমে থাকেনি। ৫২’র ভাষা আন্দোলনের বছরও ঢাকায় ফুটবল লীগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বছর বিজি প্রেস লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং ওয়ান্ডারার্স রানার্সআপ হয়। তবে বরেণ্য প্রবীন ক্রীড়া সাংবাদিক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান তার এক নিবন্ধে লিখেছেন- ‘পঞ্চাশের দশকে ফুটবলে প্রান ছিলো না। আর এই প্রানহীন, গতিহীন ফুটবলে সে সময়ের কিছু ফুটবলার প্রান ও গতি ফিরিয়ে এনেছিলেন।’ কামরুজ্জামান যাদের মধ্যে দাউদকান্দির ছেলে আশরাফ চৌধুরীকে অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, পঞ্চাশের দশকে ইপিআর-এর শওকত, ক্যাপ্টেন নেওয়াজ, বিজি প্রেসের ছুন্না রশিদ, আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের আনোয়ার, মান্না, ওয়ান্ডারার্সের বলাই, বাহারাম, মহারাজ, সেন্ট্রাল স্টেশনারীর চার্লস, জামাল, ওয়ারীর আউয়াল প্রমুখ খেলোয়াড়রদের নৈপুণ্য সে সময়ের দর্শকদের নজর কাড়ে। এ সময়টাতে আরো যারা নিজেদের ফুটবল নৈপুন্য দিয়ে এদেশের ফুটবলকে আলোকিত করেছিলেন, তাদের মধ্যে মিয়াজী, মোমতাজ, রঞ্জিত, নবী চৌধুরী, ভাওয়াল ওয়াজেদ, সাদেক, মঞ্জুর হাসান মিন্টু, কামরুজ্জামান, সিতাংশু প্রমূখের নাম উল্লেখযোগ্য। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আরো যে সব খেলোয়াড় স্বীয় নৈপুণ্য দ্বারা ফুটবলকে আলোকিত করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, গজনবী, আরজু, কবির, আশ্রাফ, শাহ আলম, আমান, পি ঘোষ, সামাদ, হুমায়ুন, নাসির, তফাজ্জল, কানু, মারি, খায়ের, নজরুল, মদন, দেবাশীষ, আবেদ, কালা গফুর, রাহি, সিদ্দিক, আম্বিয়া, হাশেম দীন, কাদিও, কাইয়ুম, চেঙ্গেজি প্রমূখ।
মো হা মে ডা নে র উ ত্থা ন
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঢাকার ফুটবলে ওয়ান্ডারার্সের একচেটিয়া আধিপত্য ছিলো। তখন ওয়ান্ডারার্স যে কতোটা অপ্রতিরোধ্য ছিলো, সেটা সে সময় লীগে তাদের পারফরমেন্সের ওপর চোখ রাখলেই পরিস্কার হয়ে যায়। ১৯৪৮ থেকে ’৫৬- এই নয় বছরের মধ্যে তারা লীগ শিরোপা জয় করেছে ৫ বার (’৫০,’৫১,’৫৩,’৫৪,’৫৬)। রানার্সআপ হয়েছে ১ বার (’৫২)। বন্যার কারণে ’৫৫ সালে লীগ মাঝ পথে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর শুরু হয় মোহামেডানের অপ্রতিরোধ্য উত্থান। এবার তাকানো যাক এই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটির জন্মলগ্নের দিকে ঃ ‘বেস্ট অব ক্রীড়ালোক’ পুস্তকে প্রকাশিত মজিবর রহমান লিখিত ‘মোহামেডান ক্লাবের ইতিহাস’ শীর্ষক লেখাটিতে এ সম্পর্কে তথ্য মেলে। কারো কারো মতে, ঢাকা মোহামেডানের জন্ম ১৯৩৮ সালে। তবে অনুসন্ধান করে ১৯৪৭ সালের ক্লাব প্যাডের একটি সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। যা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ১৯৩৮ সালে ক্লাবের জন্ম হওয়ার তথ্যটি সঠিক নয়। অপরদিকে দিলকুশার খাজা পরিবারে যে ঢাকা মোহামেডানের কার্যক্রম একসময় সচল ছিলো, তা সহজে অনুমান করা যায়। উল্লেখ্য, খাজা নাজিমউদ্দিন, খাজা নুরুদ্দিন ও বেগম নুরুদ্দিন কলকাতা মোহামেডানের নির্বাহী কমিটিতে ছিলেন। খাজা নুরুদ্দিন এক সময় কলকাতা মোহামেডানের সাধারণ সম্পাদকেরও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৭ সালের ৭ মে দিলকুশা হাউজে খাজা পরিবারের বেশ কয়েকজন ক্রীড়ানুরাগীর উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খাজা আদেল, খাজা ইসমাইল, খাজা আজাদ, খাজা সুলেমান, খাজা আতিকউল্লাহ, খাজা আজমল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। সভাপতিত্ব করেন হকির গোলরক্ষক খাজা সুলেমান। সভায় খাজা ইসমাইলকে সভাপতি ও খাজা আদেলকে সাধারণ সম্পাদক করে ‘মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাব’ নামে একটি ক্লাব গঠন করা হয়। এরপর ঢাকার হাজারীবাগের ২৫ নম্বর মনেশ্বর রোডের কাজী আউয়ালকে ফুটবল দল গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। কাজী আউয়াল ঢাকার স্কুল, কলেজ ,মাদ্রাসা ঘুরে ঘুরে একটি ফুটবল দল গঠন করেন। মুসলিম স্পোর্টিং এ বছর রোনাল্ড শিল্ডে অংশ নিয়ে দর্শকদের প্রশংসা কুড়ায়। এরপর এই ক্লাবের কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পরে। আর এভাবে বেশ ক’টি বছর গত হবার পর নবাব পরিবার আবার ক্লাবটির প্রতি মনোযোগী হয়।
পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঢাকার ফুটবলে ওয়ান্ডারার্সের একচেটিয়া আধিপত্য ছিলো। তখন ওয়ান্ডারার্স যে কতোটা অপ্রতিরোধ্য ছিলো, সেটা সে সময় লীগে তাদের পারফরমেন্সের ওপর চোখ রাখলেই পরিস্কার হয়ে যায়। ১৯৪৮ থেকে ’৫৬- এই নয় বছরের মধ্যে তারা লীগ শিরোপা জয় করেছে ৫ বার (’৫০,’৫১,’৫৩,’৫৪,’৫৬)। রানার্সআপ হয়েছে ১ বার (’৫২)। বন্যার কারণে ’৫৫ সালে লীগ মাঝ পথে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর শুরু হয় মোহামেডানের অপ্রতিরোধ্য উত্থান। এবার তাকানো যাক এই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটির জন্মলগ্নের দিকে ঃ ‘বেস্ট অব ক্রীড়ালোক’ পুস্তকে প্রকাশিত মজিবর রহমান লিখিত ‘মোহামেডান ক্লাবের ইতিহাস’ শীর্ষক লেখাটিতে এ সম্পর্কে তথ্য মেলে। কারো কারো মতে, ঢাকা মোহামেডানের জন্ম ১৯৩৮ সালে। তবে অনুসন্ধান করে ১৯৪৭ সালের ক্লাব প্যাডের একটি সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। যা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ১৯৩৮ সালে ক্লাবের জন্ম হওয়ার তথ্যটি সঠিক নয়। অপরদিকে দিলকুশার খাজা পরিবারে যে ঢাকা মোহামেডানের কার্যক্রম একসময় সচল ছিলো, তা সহজে অনুমান করা যায়। উল্লেখ্য, খাজা নাজিমউদ্দিন, খাজা নুরুদ্দিন ও বেগম নুরুদ্দিন কলকাতা মোহামেডানের নির্বাহী কমিটিতে ছিলেন। খাজা নুরুদ্দিন এক সময় কলকাতা মোহামেডানের সাধারণ সম্পাদকেরও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৭ সালের ৭ মে দিলকুশা হাউজে খাজা পরিবারের বেশ কয়েকজন ক্রীড়ানুরাগীর উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খাজা আদেল, খাজা ইসমাইল, খাজা আজাদ, খাজা সুলেমান, খাজা আতিকউল্লাহ, খাজা আজমল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। সভাপতিত্ব করেন হকির গোলরক্ষক খাজা সুলেমান। সভায় খাজা ইসমাইলকে সভাপতি ও খাজা আদেলকে সাধারণ সম্পাদক করে ‘মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাব’ নামে একটি ক্লাব গঠন করা হয়। এরপর ঢাকার হাজারীবাগের ২৫ নম্বর মনেশ্বর রোডের কাজী আউয়ালকে ফুটবল দল গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। কাজী আউয়াল ঢাকার স্কুল, কলেজ ,মাদ্রাসা ঘুরে ঘুরে একটি ফুটবল দল গঠন করেন। মুসলিম স্পোর্টিং এ বছর রোনাল্ড শিল্ডে অংশ নিয়ে দর্শকদের প্রশংসা কুড়ায়। এরপর এই ক্লাবের কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পরে। আর এভাবে বেশ ক’টি বছর গত হবার পর নবাব পরিবার আবার ক্লাবটির প্রতি মনোযোগী হয়।
১৯৩৪ সালে খাজা আজমল ও খাজা নিমরুল্লাহসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ক্লাবটির নাম পরিবর্তন করে ‘মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব’ রাখেন। জন্ম লাভের পর প্রায় দুই দশক তেমন চমকপ্রদ কিছু করতে পারেনি মোহামেডান। এর সাফল্যের রথ ছুটতে শুরু করে মূলত ১৯৫৬ সাল থেকে। এ বছরের লীগে তারা সে সময়ের ফুটবলে একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তারকারী ও আগের দু’বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ন ওয়ান্ডারার্সের শক্ত প্রতিপক্ষ হিসেবে উঠে দাঁড়ায়। যদিও সে বছর ওয়ান্ডারার্সের কাছ থেকে তারা শিরোপা ছিনিয়ে নিতে পারেনি, রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। কিন্তু এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে ওয়ান্ডারার্সকে পরাভূত করে প্রথমবারের মতো লীগ শিরোপার স্বাদ গ্রহণ করে মোহামেডান। সেই যে সাফল্যের শুরু আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি এই ক্লাবটিকে। আজও সে এগিয়ে চলছে শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার নিয়ে আপন আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয়ে। ষাটের পুরো দশক জুড়েই মোহামেডানের এই আধিপত্য বলতে গেলে অক্ষুন্ন থাকে। এ সময়ে অবশ্য ঢাকার অন্যতম প্রবীণ ক্লাব ভিক্টোরিয়া ও ইপিআইডিসি মোহামেডানের বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে বার কয়েক দাঁড়ায় বটে, তবে তা ছিলো সাময়িক।
পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে ঢাকার ফুটবলে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব, আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব, বিজি প্রেস, ইপিআইডিসি দলগুলো শক্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতো। ঢাকা লীগের পাশাপাশি স্বাধীনতা দিবস ফুটবল, আগা খান গোল্ড কাপের জমজমাট আসর বসতো। এছাড়া বগুড়ায় মোহাম্মদ আলী কাপ, কুমিল্লায় রকিবউদ্দিন গোল্ড কাপ, গাইবান্ধায় খান বাহাদুর শিল্ড, রংপুরে গোবিন্দলার শিল্ড, ময়মনসিংহের ‘সূর্যকান্ত শিল্ড’, দিনাজপুরের নরনারায়ণ রামকানাই কুন্ড শিল্ড’-এর প্রতিযোগিতাগুলো জমজমাটভাবে অনুষ্ঠিত হতো। চট্রগ্রামের ফুটবলও ছিলো সরগরম।
মু ক্তি যু দ্ধে ফু ট ব ল
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনে ফুটবলের রয়েছে অসামান্য অবদান। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে বসে থাকেননি ফুটবলাররাও। প্রিয় বাংলাদেশকে শত্রমুক্ত করতে তারাও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সুদৃঢ় প্রত্যয়ে যখন দেশের প্রদীপ্ত তরুণেরা হাতে তুলে নিয়েছিলো অস্ত্র, তখন বাংলাদেশের একঝাঁক তরুণ ফুটবলার খেলার মাঠে গড়ে তুলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের আর এক ফ্রন্ট। গঠন করেছিলেন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল। তারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছেন, সংগ্রহ করেছেন জনমত এবং অর্থ। সে সময় প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ভারতীয় মুদ্রায় তিন লাখ টাকা তুলে দিয়েছিলো তৎকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের হাতে। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ভারতের বিভিন্ন স্থানে মোট ১৬টি খেলায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ১২টিতে জয়ী, ৩টিতে পরাজিত হয় ও ১টি খেলা ড্র করে। ১৯৭১ সালের ২৪ জুলাই স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ভারতে তাদের প্রথম ম্যাচটি খেলে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর কালেক্টরেট মাঠে কৃষ্ণনগর একাদশের বিরুদ্ধে। ঐ ম্যাচের পূর্বে স্বাধীন বাংলার ফুটবল সৈনিকরা প্রথম বিদেশের মাঠে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলো এবং জাতীয় সঙ্গিত বাজিয়েছিলো।। এ সময় অবশ্য একটা জটিলতার সৃষ্টি হযেছিলো, যেহেতু ভারত সরকার তখন পর্যন্ত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি সেহেতু নদীয়া জেলা প্রশাসন জোর আপত্তি তুললো স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর ব্যাপারে। এদিকে বেঁকে বসলো স্বাধীন বাংলা একাদশ, তাদেও কথা একটাই- ’পতাকা উত্তোলন না করা হলে এবং জাতীয় সঙ্গীত না বাজানো হলে আমরা মাঠে নামবো না।’ পরে মুক্তিকামী খেলোয়াড়দের কাছে নতি স্বীকার করে নদীয়া জেলা প্রশাসন। ভারতের জাতীয় পতাকার পাশে যখন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হয় তখন বাজানো হয় দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত। খেলাটি ২-২ গোলে অমীমাংসিত থাকে। এরপর স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ৮ আগস্ট মোহনবাগান মাঠে গোস্টপাল একাদশের বিরুদ্ধে খেলে। উল্লেখ্য, গোস্টপাল একাদশ ছিলো মূলত মোহনবাগানের সেরা একাদশের ধারণকৃত নাম। এ খেলায় তারা ২-৪ গোলে গোস্টপাল একাদশের কাছে পরাজিত হয়। ১৪ আগস্ট কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর মাঠে দক্ষিণ কলকাতা স্পোর্টস ফেডারেশনের বিরুদ্ধে তারা ৪-২ গোলে জয়ী হয় সফরকারী দল। পশ্চিমবঙ্গের রামকৃষ্ণ মিশনে নরেন্দ্রপুর একাদশের বিরুদ্ধে ৪র্থ ম্যাচ খেলে স্বাধীন বাংলা ফুটবল একাদশ। এ খেলায় তারা জয়ী হয় ২-০ গোলে। এর ক’দিন পর দলটি বর্ধমান একাদশের বিরুদ্ধে মাঠে নামে। পরবর্তীতে বানারস, বিহার প্রদেশের সিওয়ান, ফখরপুর, দুর্গাপুর, বানপুর, চিত্তরঞ্জন, মালদহ, বালুরঘাট, বোম্বে প্রভৃতি স্থানে প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ নেয়। তবে এর মধ্যে বোম্বের খেলাটি ছিলো সবচাইতে আকর্ষণীয় ও জমজমাট। এখানে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল মহারাষ্ট্র একাদশের বিরুদ্ধে খেলতে নামে। এ খেলায় মহারাষ্ট্র একাদশের অধিনায়ক ছিলেন ভারতের এককালের তুখোড় ক্রিকেটার পতৌদির নবাব মনসুর আলী। আর বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ফুটবলারদের উৎসাহিত করতে এদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন বোম্বের পর্দা কাঁপানো অভিনেতা-অভিনেত্রী দিলীপ কুমার, শর্মিলা ঠাকুর, রাজেশ খান্না, মোমতাজ, বিশ্বজিৎ প্রমুখ। খেলায় স্বাধীন বাংলা একাদশ ৩-২ গোলে মহারাষ্ট্র একাদশকে পরাজিত করে। ভারত সফরকালে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলটি প্রতিটি ম্যাচের পূর্বে প্রিয় জন্মভূমির পতাকা হাতে মাঠ প্রদক্ষিণ করে। এ সময় ভারতের যেখনেই খেলতে গেছে সেখানেই এই মুক্তিকামী ফুটবলাররা পেয়েছে বিপুল সংবর্ধনা আর উচ্ছ্বাসভরা উৎসাহ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ফুটবলারদের এ ভূমিকা চিরদিন অম্লাণ হয়ে থাকবে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে মুক্তিযোদ্ধা ফুটবলারদেরও। এবার এক নজরে তাকানো যাক এ দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তার তালিকাটির দিকে- ১ম সভাপতি- শামসুল হক (তৎকালীন মন্ত্রী), ২য় সভাপতি-আশরাফ আলী চৌধুরী, তৃতীয় সভাপতি- এন এ চৌধুরী (কালু ভাই)। ম্যানেজার- তানভির মাজহারুল ইসলাম তান্না, কোচ- ননী বসাক, অধিনায়ক- জাকারিয়া পিন্টু, সহঃঅধিনায়ক- প্রতাপ শংকর হাজরা, খেলোয়াড়- মোঃ নুরুন্নবী, আইনুল হক, শাজাহান আলম, আলী ইমাম, লালু, মোঃ কায়কোবাদ, সুভাষ চন্দ্র সাহা, অমলেস সেন, শেখ আশরাফ আলী, এনায়েতুর রহমান, সাইদুর রহমান প্যাটেল, বিমল কর, তসলিম, অনিরুদ্ধ, মোমিন, খোকন, কাজী সালাহউদ্দিন, নওসুরুজ্জামান, সুরুজ, আব্দুল হাকিম, শিহাব, লুৎফর রহমান, গোবিন্দ কুন্ড, সঞ্জিত, মহিবুর রহমান, সাত্তার, পেয়ারা, মাহমুদ ও মোজাম্মেল।
আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনে ফুটবলের রয়েছে অসামান্য অবদান। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে বসে থাকেননি ফুটবলাররাও। প্রিয় বাংলাদেশকে শত্রমুক্ত করতে তারাও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সুদৃঢ় প্রত্যয়ে যখন দেশের প্রদীপ্ত তরুণেরা হাতে তুলে নিয়েছিলো অস্ত্র, তখন বাংলাদেশের একঝাঁক তরুণ ফুটবলার খেলার মাঠে গড়ে তুলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের আর এক ফ্রন্ট। গঠন করেছিলেন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল। তারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছেন, সংগ্রহ করেছেন জনমত এবং অর্থ। সে সময় প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ভারতীয় মুদ্রায় তিন লাখ টাকা তুলে দিয়েছিলো তৎকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের হাতে। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ভারতের বিভিন্ন স্থানে মোট ১৬টি খেলায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ১২টিতে জয়ী, ৩টিতে পরাজিত হয় ও ১টি খেলা ড্র করে। ১৯৭১ সালের ২৪ জুলাই স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ভারতে তাদের প্রথম ম্যাচটি খেলে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর কালেক্টরেট মাঠে কৃষ্ণনগর একাদশের বিরুদ্ধে। ঐ ম্যাচের পূর্বে স্বাধীন বাংলার ফুটবল সৈনিকরা প্রথম বিদেশের মাঠে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলো এবং জাতীয় সঙ্গিত বাজিয়েছিলো।। এ সময় অবশ্য একটা জটিলতার সৃষ্টি হযেছিলো, যেহেতু ভারত সরকার তখন পর্যন্ত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি সেহেতু নদীয়া জেলা প্রশাসন জোর আপত্তি তুললো স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর ব্যাপারে। এদিকে বেঁকে বসলো স্বাধীন বাংলা একাদশ, তাদেও কথা একটাই- ’পতাকা উত্তোলন না করা হলে এবং জাতীয় সঙ্গীত না বাজানো হলে আমরা মাঠে নামবো না।’ পরে মুক্তিকামী খেলোয়াড়দের কাছে নতি স্বীকার করে নদীয়া জেলা প্রশাসন। ভারতের জাতীয় পতাকার পাশে যখন স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হয় তখন বাজানো হয় দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত। খেলাটি ২-২ গোলে অমীমাংসিত থাকে। এরপর স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ৮ আগস্ট মোহনবাগান মাঠে গোস্টপাল একাদশের বিরুদ্ধে খেলে। উল্লেখ্য, গোস্টপাল একাদশ ছিলো মূলত মোহনবাগানের সেরা একাদশের ধারণকৃত নাম। এ খেলায় তারা ২-৪ গোলে গোস্টপাল একাদশের কাছে পরাজিত হয়। ১৪ আগস্ট কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর মাঠে দক্ষিণ কলকাতা স্পোর্টস ফেডারেশনের বিরুদ্ধে তারা ৪-২ গোলে জয়ী হয় সফরকারী দল। পশ্চিমবঙ্গের রামকৃষ্ণ মিশনে নরেন্দ্রপুর একাদশের বিরুদ্ধে ৪র্থ ম্যাচ খেলে স্বাধীন বাংলা ফুটবল একাদশ। এ খেলায় তারা জয়ী হয় ২-০ গোলে। এর ক’দিন পর দলটি বর্ধমান একাদশের বিরুদ্ধে মাঠে নামে। পরবর্তীতে বানারস, বিহার প্রদেশের সিওয়ান, ফখরপুর, দুর্গাপুর, বানপুর, চিত্তরঞ্জন, মালদহ, বালুরঘাট, বোম্বে প্রভৃতি স্থানে প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ নেয়। তবে এর মধ্যে বোম্বের খেলাটি ছিলো সবচাইতে আকর্ষণীয় ও জমজমাট। এখানে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল মহারাষ্ট্র একাদশের বিরুদ্ধে খেলতে নামে। এ খেলায় মহারাষ্ট্র একাদশের অধিনায়ক ছিলেন ভারতের এককালের তুখোড় ক্রিকেটার পতৌদির নবাব মনসুর আলী। আর বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা ফুটবলারদের উৎসাহিত করতে এদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন বোম্বের পর্দা কাঁপানো অভিনেতা-অভিনেত্রী দিলীপ কুমার, শর্মিলা ঠাকুর, রাজেশ খান্না, মোমতাজ, বিশ্বজিৎ প্রমুখ। খেলায় স্বাধীন বাংলা একাদশ ৩-২ গোলে মহারাষ্ট্র একাদশকে পরাজিত করে। ভারত সফরকালে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলটি প্রতিটি ম্যাচের পূর্বে প্রিয় জন্মভূমির পতাকা হাতে মাঠ প্রদক্ষিণ করে। এ সময় ভারতের যেখনেই খেলতে গেছে সেখানেই এই মুক্তিকামী ফুটবলাররা পেয়েছে বিপুল সংবর্ধনা আর উচ্ছ্বাসভরা উৎসাহ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ফুটবলারদের এ ভূমিকা চিরদিন অম্লাণ হয়ে থাকবে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে মুক্তিযোদ্ধা ফুটবলারদেরও। এবার এক নজরে তাকানো যাক এ দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তার তালিকাটির দিকে- ১ম সভাপতি- শামসুল হক (তৎকালীন মন্ত্রী), ২য় সভাপতি-আশরাফ আলী চৌধুরী, তৃতীয় সভাপতি- এন এ চৌধুরী (কালু ভাই)। ম্যানেজার- তানভির মাজহারুল ইসলাম তান্না, কোচ- ননী বসাক, অধিনায়ক- জাকারিয়া পিন্টু, সহঃঅধিনায়ক- প্রতাপ শংকর হাজরা, খেলোয়াড়- মোঃ নুরুন্নবী, আইনুল হক, শাজাহান আলম, আলী ইমাম, লালু, মোঃ কায়কোবাদ, সুভাষ চন্দ্র সাহা, অমলেস সেন, শেখ আশরাফ আলী, এনায়েতুর রহমান, সাইদুর রহমান প্যাটেল, বিমল কর, তসলিম, অনিরুদ্ধ, মোমিন, খোকন, কাজী সালাহউদ্দিন, নওসুরুজ্জামান, সুরুজ, আব্দুল হাকিম, শিহাব, লুৎফর রহমান, গোবিন্দ কুন্ড, সঞ্জিত, মহিবুর রহমান, সাত্তার, পেয়ারা, মাহমুদ ও মোজাম্মেল।
স্বা ধী ন তা র প র ফু ট ব ল
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) স্বাধীনতার সোনালী আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ফুটবলও নতুন পরিচয়ে, নব উদ্দমে যাত্রা শুরু করে। এরপর থেকেই ফুটবল ধাবিত হতে থাকে এক স্বর্ণালী অধ্যায় রচনার লক্ষ্যে। সত্তর এবং আশির দশকের সেই জমজমাট ফুটবল এখন যেনো শুধুই স্মৃতি। যারা সে সময় ফুটবলের সেই মেজাজ, সেই রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন- সেদিনের সেই বর্ণাঢ্য স্মৃতি মনে করে তারা আজ বুকচেরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে থাকেন। এ সময়ে ঢাকার দলগুলো যেমন যৌবন জোয়ারে ফুলে ফেঁপে উঠেছিলো তেমনি ঢাকার মাঠও ছিলো উচ্চ মানসম্পন্ন খেলোয়াড়দের দখলে। আর এসব খেলোয়াড়ের নাম ছড়িয়ে ছিলো নগর-জনপদে মানুষের মুখে মুখে। এদের খেলা দেখার জন্য স্টেডিয়ামে দর্শকদের ঢল নামতো।
স্বাধীনতার সোনালী আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ফুটবলও নতুন পরিচয়ে, নব উদ্দমে যাত্রা শুরু করে। এরপর থেকেই ফুটবল ধাবিত হতে থাকে এক স্বর্ণালী অধ্যায় রচনার লক্ষ্যে। সত্তর এবং আশির দশকের সেই জমজমাট ফুটবল এখন যেনো শুধুই স্মৃতি। যারা সে সময় ফুটবলের সেই মেজাজ, সেই রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন- সেদিনের সেই বর্ণাঢ্য স্মৃতি মনে করে তারা আজ বুকচেরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে থাকেন। এ সময়ে ঢাকার দলগুলো যেমন যৌবন জোয়ারে ফুলে ফেঁপে উঠেছিলো তেমনি ঢাকার মাঠও ছিলো উচ্চ মানসম্পন্ন খেলোয়াড়দের দখলে। আর এসব খেলোয়াড়ের নাম ছড়িয়ে ছিলো নগর-জনপদে মানুষের মুখে মুখে। এদের খেলা দেখার জন্য স্টেডিয়ামে দর্শকদের ঢল নামতো।
স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ঢাকার লীগ মাঠে গড়ালেও মাঝ পথে তা বন্ধ হয়ে যায়। ‘৭৩ সালে প্রথম সুসম্পন্ন লীগে স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়নের স্বাদ গ্রহণ করে বিআইডিসি এবং যৌথভাবে রানার্সআপ হয় মোহামেডান, আবাহনী ও ওয়ান্ডারার্স। ১৯৭২ সালে এ দেশের ফুটবলে আবাহনী ক্রীড়া চক্র নামের এক নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় ছেলে শেখ কামাল একঝাঁক প্রদীপ্ত ক্রীড়ানুরাগী যুবককে নিয়ে এ ক্লাবটি গড়ে তোলেন। আপন শক্তিমত্তার পরিচয় দিযে খুব অল্প সময়ে এ ক্লাব উঠে আসে সাফল্যের শিখরে। পরিণত হয় একটি সেরা সংগঠনে। শুধু তাই নয়, আবাহনী ক্রীড়াচক্রকে বলা হয় এদেশে আধুনিক ফুটবলের প্রবর্তক। ক্লাবটি আনুষ্ঠানিকতার প্রবর্তন করে দেশীয় ফুটবলে এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করে। জন্মলাভের পর থেকেই এ ক্লাবটি দোর্দন্ড দাপটে এগুতে থাকে সমুখের পানে, যা আজো অব্যাহত আছে। লীগে তাদের সাফল্য দেখলে মনে হয়, তারা যেনো লীগ শিরোপার দাবীদার হয়েই জন্মলাভ করেছে। ’৭২-এ জন্ম নিয়ে ’৭৩-এ রানার্সআপ এবং‘৭৪-এ চ্যাম্পিয়ন! সত্তুর-আশির দশকে মোহামেডান ও আবাহনীর দ্বিমুখী দাপটের পাশাপাশি ওয়ান্ডারার্স, দিলকুশা, বিজেএমসি, রহমতগঞ্জ, ব্রাদার্স দলগুলোর শক্তিমত্তাও ছিলো চোখে পড়ার মতো। তবে ’৭৫ সালে প্রথম বিভাগে ব্রাদার্স ইউনিয়নের আবির্ভাবের পর ঢাকার ফুটবল ত্রিমুখী লড়াইয়ের আবর্তে পতিত হয়। ব্রাদার্স এদেশের অন্যতম একটি পুরনো ক্লাব হলেও এর প্রচার এবং প্রসার ঘটে মূলত ৭৫-এর পরে। ১৯৪৯ সালে ঢাকার গোপীবাগ এলাকায় ক্রীড়ানুরাগী রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, হেলালউদ্দিন, মিজানুর রহমান, লতিফ মোল্লা প্রমূখ স্বনামধ্য ব্যাক্তিবর্গের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ক্লাবটি। এরপর দীর্ঘসময় ক্লাবটির কোনো কার্যক্রম ছিলো না বললেই চলে। ’৭৩ সালে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ছিলো তৃতীয় বিভাগের একটি দল। ঐ বছর তৃতীয় বিভাগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে দ্বিতীয় বিভাগে এবং পরের বছর দ্বিতীয় বিভাগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ’৭৫-এ প্রথম বিভাগ ফুটবলে পা রাখে। এবং এরপর থেকে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলে দিনবদলের সাথে সাথে তৃতীয় শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। ’৭২ থেকে নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত লীগের গতি ছিলো বিরতিহীন। সে সময় প্রতি বছর লীগের আয়োজন মানেই ছিলো যেনো জমজমাট ফুটবল উৎসব। আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে শুধু ঢাকা নয়, গোটা দেশে বয়ে যেতো ফুটবলের জোয়ার। লীগের বড় ম্যাচগুলো দেখার জন্য দেশের বিভিন্ন জনপদ থেকে ভক্ত-সমর্থকরা ছুটে আসতো ঢাকায়। তারা গ্যালারীতে সমবেত হয়ে নিজ দল ও খেলোয়াড়দের জোগাতো উৎসাহ। আর আবাহনী, মোহামেডান কিংবা ব্রাদার্সের খেলায় তো এক কথায় স্টেডিয়াম পরিগ্রহ করতো জনসমুদ্রের রূপ। উত্তেজনায় ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে থাকতো ফুটবলামোদীরা। ঘরে-বাইরে, হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাটে একটি প্রশ্নকে ঘিরে চলতো একই আলোচনা, ‘কে জিতবে আজকের খেলায়?’
দেশের বিভিন্ন এলাকায় ধারাবিবরণী শোনার জন্য রেডিও সেটের সামনে ভীড় করতো ফুটবলানুরাগীরা। যদি টিভিতে খেলা দেখানো হতো তবে টিভি সেটের সামনে জড়ো হতো দর্শকরা। আর যেদিন আবাহনী-মোহামেডানের লড়াই হতো সেদিন যেনো গোটা দেশের চেহারাই পাল্টে যেতো। অফিস-আদালত, বাস-লঞ্চ-ট্রেন, হোটেল- রেস্তোরা সর্বত্র চলতো একই আলোচনা। প্রিয় দলের জয়-পরাজয়ের প্রশ্নে ভক্ত-সমর্থকরা মেতে উঠতো বিতর্কে। স্টেডিয়াম এলাকা জেগে উঠতো সাজ সাজ রবে। ব্যানার-ফেস্টুনে ভরে ওঠা গ্যালারী ক্ষণে ক্ষণে ফেটে পড়তো ‘গোল’, ‘গোল’ চিৎকারে। এদেশের ফুটবলে মোহামেডানের আধিপত্য বলতে গেলে যখন ছিলো একচ্ছত্র ঠিক তখন মোহামেডানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয় আবাহনী ক্রীড়াচক্র। আবাহনীর আবির্ভাব মূলত দেশীয় ফুটবলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়েছে, বাড়িয়েছে আকর্ষণ আর দর্শক। সংযোজিত হয়েছে একটা তীব্র প্রতিযোগিতার ধারা। বলার অপেক্ষা রাখে না, এতে প্রধান দুটি দল হিসেবে যেমন মোহামেডান-আবাহনীর বিশাল সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে পাশাপাশি ফুটবলেরও ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হযেছে। ফুটবলে যোগ হযেছে নবতর কলা-কৌশল। এসেছেন বিদেশী প্রশিক্ষক এবং খেলোয়াড়। কলাকৌশলের আধুনিক প্রয়োগ, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মেজাজ, জয় ছিনিয়ে নেয়ার অদম্য বাসনা- সব মিলিয়ে আবাহনী-মোহামেডানের ফুটবল মানেই ছিলো যেনো জ্বলে ওঠা বারুদ। তখন ছোট দলগুলোও লড়তো সেয়ানের মতো। ছিলো না পাতানো খেলার গন্ধও। সেই দিনগুলোকে আজ মনে হয় স্বপ্ন। ’৭৩ থেকে ’৯০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৭টি লীগের মধ্যে মোহামেডান ৭ বার, আবাহনী ৮ বার, বিআইডিসি ১ বার, এবং বিজেএমসি একবার করে শিরোপা জয় করে। এর মধ্যে আবাহনী একবার (’৮৩,’৮৪,’৮৫) এবং মোহামেডান একবার (’৮৬, ’৮৭, ’৮৮-৮৯) হ্যাট্রিক শিরোপার স্বাদ পায়। এ সময়ে একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, ’৭৫-এ লীগের আঙ্গিনায় পা রাখার পর থেকে প্রতিটি আসরে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে লড়াই করলেও একবারো লীগ শিরোপার স্বাদ পায়নি ব্রাদার্স ইউনিয়ন। তারা তৃতীয় শক্তি হিসেবেই যেনো স্থায়ী আসন করে নিয়েছিলো। তবে এখানে একটি তথ্য দেয়া দরকার। আর তা হচ্ছে, ‘৭৫-এর পর থেকে যে স্বপ্ন লালন করে আসছিলো ব্রাদার্স, দুই যুগেরও বেশী সময় অপেক্ষার পর অবশেষে তাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। ২০০৩ সালে তারা পেয়েছে প্রথম লীগ শিরোপার স্বাদ। নব্বই দশকের শেষদিকে লীগের দাবীদার হিসেবে উথ্থান ঘটে মুক্তিযোদ্ধা ক্রীড়া চক্রের। উল্লেখ্য, এই দলটি ১৯৯৭ সালে প্রথম লীগ শিরোপার স্বাদ পায়। এখানে আরও একটি তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন, আর তা হচ্ছে, ’৭২ থেকে ’৭৮ পর্যন্ত লীগ অনুষ্ঠিত হতো বাফুফে’র অধীনে। ’৭৯ সাল থেকে তা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পায় ডামফা কর্তৃপক্ষ। কোথায় হারিয়ে গেলো সেসব দিন, আর কোথায়ই বা হারিয়ে গেলো সেই ফুটবল? কেনো আজ ফুটবলের করুণ চিত্র? আসলে ফুটবল মূলত দলাদলির বলি হয়েছে। একদিকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, অপরদিকে ঢাকা স্টেডিয়াম টু মিরপুর স্টেডিয়াম টানাহ্যাঁচড়া ফুটবলের বারোটা বাজিয়েছে। আর সেই সাথে বারোটা বেজেছে গোটা দেশের ফুটবলেরও। কেননা ঢাকায় ফুটবল অনুষ্ঠিত হলে এর রেশ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, ঢাকার ফুটবলের অবনতির সাথে সাথে বিভিন্ন জেলাতেও ফুটবলের অবনতি ঘটেছে। এখন জেলা স্টেডিয়ামগুলো সারা বছরই হয় শূন্য থাকে, নয়তো গোচারণভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে ফুটবল মৃতপ্রায় বলে বিভিন্ন জেলায় লীগ ও অন্য টুর্নামেন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সারা দেশেই ফুটবল কফিনবন্দী হয়ে পড়েছে। অপরদিকে ফুটবলারদের মানও পড়ে গেছে। আর মান কমে যাওয়ার ফলে ফুটবলারদের ব্যক্তিগত ইমেজও কমে গেছে। আগে যেমন সালাহউদ্দিন, এনায়েত, চুন্নু, এমিলি, গাফ্ফার, সালাম মুর্শেদী, বাদল রায়, খুরশীদ বাবুল, আসলাম, নান্নু, মঞ্জ, টুটুলদের খেলা দেখার জন্য দর্শকরা মাঠে ছুটে যেতো কিন্তু আজ তেমনভাবে কোনো খেলোয়াড়ই দর্শকদের মাঠে টানতে পারছেন না।
মি র পু রে ফু ট ব ল
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) ১৯৮৭-৮৮ সালে ফুটবলের যখন স্বর্ণযুগ চলছিলো তখনই প্রথম ফুটবলের ওপর আঘাত আসে। ফুটবলকে ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় মিরপুর স্টেডিয়ামে। যাতায়াত সমস্যা, নিরাপত্তার প্রশ্ন, বাড়তি খরচের বোঝা ইত্যাদি নানা কারণে দর্শকরা মিরপুর পর্যন্ত যেতে অনাগ্রহী হয়ে ওঠে। এতে ফুটবলের দর্শক সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যেতে থাকে। আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয় এই জনপ্রিয় খেলাটি। ব্যাপারটি অনুধাবন করতে পেরে কর্তৃপক্ষ আবার ফুটবলকে ফিরিয়ে আনে ঢাকা স্টেডিয়ামে। আবার ফুটবলের আঙিনা আলোয় ঝলমল করে ওঠে। এরপর ’৯৫ পর্যন্ত ফুটবল ঢাকা স্টেডিয়ামেই ছিলো। এই সময়কালেও ফুটবলের রঙ ছিলো, দর্শকদের আকর্ষণ ছিলো। দর্শকরা ফুটবলের টানে ছুটে আসতো ঢাকা স্টেডিয়ামে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৯৩ সালে লীগে মোট টিকিট বিক্রি হয়েছিলো ১ কোটি ২৬ লাখ ৬০ হাজার ৮শ’ টাকার। এর মধ্যে মোহামেডান-আবাহনীর মধ্যকার লীগের শেষ ম্যাচটিতে টিকিট বিক্রির পরিমান ছিলো ৪ লাখ ৬০ হাজার ৮শ’ টাকা। আর মিরপুর স্টেডিয়ামে ফুটবলকে নির্বাসিত করার পর পনের ভাগের একভাগও টিকিট বিক্রি নেই। কোনো কোনো ম্যাচে দর্শক খরা দেখলে তো কষ্ট লাগে। শূন্য গ্যালারী দেখে মনে প্রশ্ন জাগে, এই কি আমাদের সেই ফুটবল? আবার অন্যদিকে স্পন্সররাও মিরপুরে যেতে চায় না। অথচ ঢাকা স্টেডিয়ামে বড় অঙ্কের স্পন্সর পেতে কোনো সমস্যাই হতো না। লীগের পর ১৯৮০ সালে শুরু হওয়া ফেডারেশন কাপকে ঘিরে আর এক উত্তেজনায় মেতে উঠতো ফুটবলামোদীরা। আজ সে আসরেরও নেই উত্তাপ-উত্তেজনা। যদিও বর্তমানে স্থায়ীভাবে ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ফুটবলকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে তবে সেই রূপ আর মেজাজ এখন আর প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না। দর্শকও সেভাবে আর মাঠে আসছে না। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এখন আবাহনী-মোহামেডানের খেলাতেও গ্যালারী থাকে দর্শকশূন্য।
১৯৮৭-৮৮ সালে ফুটবলের যখন স্বর্ণযুগ চলছিলো তখনই প্রথম ফুটবলের ওপর আঘাত আসে। ফুটবলকে ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় মিরপুর স্টেডিয়ামে। যাতায়াত সমস্যা, নিরাপত্তার প্রশ্ন, বাড়তি খরচের বোঝা ইত্যাদি নানা কারণে দর্শকরা মিরপুর পর্যন্ত যেতে অনাগ্রহী হয়ে ওঠে। এতে ফুটবলের দর্শক সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যেতে থাকে। আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয় এই জনপ্রিয় খেলাটি। ব্যাপারটি অনুধাবন করতে পেরে কর্তৃপক্ষ আবার ফুটবলকে ফিরিয়ে আনে ঢাকা স্টেডিয়ামে। আবার ফুটবলের আঙিনা আলোয় ঝলমল করে ওঠে। এরপর ’৯৫ পর্যন্ত ফুটবল ঢাকা স্টেডিয়ামেই ছিলো। এই সময়কালেও ফুটবলের রঙ ছিলো, দর্শকদের আকর্ষণ ছিলো। দর্শকরা ফুটবলের টানে ছুটে আসতো ঢাকা স্টেডিয়ামে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৯৩ সালে লীগে মোট টিকিট বিক্রি হয়েছিলো ১ কোটি ২৬ লাখ ৬০ হাজার ৮শ’ টাকার। এর মধ্যে মোহামেডান-আবাহনীর মধ্যকার লীগের শেষ ম্যাচটিতে টিকিট বিক্রির পরিমান ছিলো ৪ লাখ ৬০ হাজার ৮শ’ টাকা। আর মিরপুর স্টেডিয়ামে ফুটবলকে নির্বাসিত করার পর পনের ভাগের একভাগও টিকিট বিক্রি নেই। কোনো কোনো ম্যাচে দর্শক খরা দেখলে তো কষ্ট লাগে। শূন্য গ্যালারী দেখে মনে প্রশ্ন জাগে, এই কি আমাদের সেই ফুটবল? আবার অন্যদিকে স্পন্সররাও মিরপুরে যেতে চায় না। অথচ ঢাকা স্টেডিয়ামে বড় অঙ্কের স্পন্সর পেতে কোনো সমস্যাই হতো না। লীগের পর ১৯৮০ সালে শুরু হওয়া ফেডারেশন কাপকে ঘিরে আর এক উত্তেজনায় মেতে উঠতো ফুটবলামোদীরা। আজ সে আসরেরও নেই উত্তাপ-উত্তেজনা। যদিও বর্তমানে স্থায়ীভাবে ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ফুটবলকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে তবে সেই রূপ আর মেজাজ এখন আর প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না। দর্শকও সেভাবে আর মাঠে আসছে না। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এখন আবাহনী-মোহামেডানের খেলাতেও গ্যালারী থাকে দর্শকশূন্য।
ফু ট ব লে র কাঁ ধে ক্রি কে টে র ভূ ত
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে থাকেন যে, দিনে দিনে ক্রিকেটের ভূত এমনভাবে ফুটবলের ওপর চেপে বসেছে- যা ফুটবলের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে চলেছে। বিশেষ করে ক্রিকেটের কারণেই ফুটবল ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে বিতাড়িত হয়েছিলো। আবারো হবার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ফুটবলের মিরপুরে নির্বাসন প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সোনালী অতীতের ফুটবলার বাদল রায় ‘৯৮ সালে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসর পর ক্রিকেটের উন্নয়নের জন্য ক্রীড়ামন্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে আমরা প্রথম বছর অর্থাৎ ’৯৬ সালে লীগ মিরপুরে অনুষ্ঠিত করি। কিন্তু তাতে আমরা দারুণভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হই। খেলোয়াড়দের গুণগত মান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নিরাপত্তার কারণে ফুটবল মিরপুরে দর্শক টানতে ব্যর্থ হয়।’ ১৯৯৭ সালে জাতীয় ক্রিকেট দল আইসিসি ট্রফি জয় করলে সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তারা অনেকটা ধাক্কা মেরে ফুটবলকে খাঁদে ফেলে দেন। এরপর ক্রিকেটের ওয়ানডে ও টেস্ট স্ট্যাটাস প্রাপ্তিতে আবেগপ্রবণ কর্মকর্তাদের ক্রিকেটের প্রতি আবেগ আরো বেড়ে গেলো। সরকার বদলালেও ফুটবলের ভাগ্য বদলালো না। অনেক ক্ষেত্রে ফুটবল বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার হতে থাকে। দিনে দিনে নদীর পানি গড়িয়েছে অনেক, এরই মাঝে ফুটবল আবার ফিরে এসেছে তার পুরনো ঠিকানায়, তবে আসল বাস্তবতা হচ্ছে, ফুটবল আজও পারছেনা কাঁধ থেকে ক্রিকেটের ভূতটাকে নামিয়ে ফেলতে। তবে সচেতন মহলের এক কথা, ক্রিকেট নিয়ে যতোই মাতামাতি করা হোক না কেনো, ৬৮ হাজার গ্রাম বাঁচলে যেমন বাংলাদেশ বাঁচবে, তেমনি ফুটবল বাঁচলেই এদেশের সকল খেলাধুলা বাঁচবে।
একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে থাকেন যে, দিনে দিনে ক্রিকেটের ভূত এমনভাবে ফুটবলের ওপর চেপে বসেছে- যা ফুটবলের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে চলেছে। বিশেষ করে ক্রিকেটের কারণেই ফুটবল ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে বিতাড়িত হয়েছিলো। আবারো হবার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ফুটবলের মিরপুরে নির্বাসন প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সোনালী অতীতের ফুটবলার বাদল রায় ‘৯৮ সালে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসর পর ক্রিকেটের উন্নয়নের জন্য ক্রীড়ামন্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে আমরা প্রথম বছর অর্থাৎ ’৯৬ সালে লীগ মিরপুরে অনুষ্ঠিত করি। কিন্তু তাতে আমরা দারুণভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হই। খেলোয়াড়দের গুণগত মান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নিরাপত্তার কারণে ফুটবল মিরপুরে দর্শক টানতে ব্যর্থ হয়।’ ১৯৯৭ সালে জাতীয় ক্রিকেট দল আইসিসি ট্রফি জয় করলে সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তারা অনেকটা ধাক্কা মেরে ফুটবলকে খাঁদে ফেলে দেন। এরপর ক্রিকেটের ওয়ানডে ও টেস্ট স্ট্যাটাস প্রাপ্তিতে আবেগপ্রবণ কর্মকর্তাদের ক্রিকেটের প্রতি আবেগ আরো বেড়ে গেলো। সরকার বদলালেও ফুটবলের ভাগ্য বদলালো না। অনেক ক্ষেত্রে ফুটবল বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার হতে থাকে। দিনে দিনে নদীর পানি গড়িয়েছে অনেক, এরই মাঝে ফুটবল আবার ফিরে এসেছে তার পুরনো ঠিকানায়, তবে আসল বাস্তবতা হচ্ছে, ফুটবল আজও পারছেনা কাঁধ থেকে ক্রিকেটের ভূতটাকে নামিয়ে ফেলতে। তবে সচেতন মহলের এক কথা, ক্রিকেট নিয়ে যতোই মাতামাতি করা হোক না কেনো, ৬৮ হাজার গ্রাম বাঁচলে যেমন বাংলাদেশ বাঁচবে, তেমনি ফুটবল বাঁচলেই এদেশের সকল খেলাধুলা বাঁচবে।
আ ন্ত র্জা তি ক ম য় দা নে আ মা দে র ফু ট ব ল
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) সত্তর-আশির দশকে ঢাকার ফুটবল সবসময়ই সরগরম থাকতো। আগা খান গোল্ড কাপকে ঘিরে বসতো জমজমাট আন্তর্জাতিক ফুটবল। প্রেসিডেন্ট গোল্ড কাপের আন্তর্জাতিক ফুটবল উৎসবে মেতে উঠতো ফুটবলামোদীরা। উল্লেখ্য, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট গোল্ডকাপের শিরোপা জয় করেছিলো বাংলাদেশ আর সেটাই আন্তর্জাতিক ফুটবলে আমাদের অর্জিত প্রথম ট্রফি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশের অবস্থান মোটেও ভালো নয়। আগের সাতটি আসরে নাকানি-চুবানি খেয়ে, বছরের পর বছর অপেক্ষা করে ১৯৯৯ সালে কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত অষ্টম সাফ গেমস ফুটবলে সোনা পেয়েছে বাংলাদেশ। তবে ঐ একবারই। এরপর আর নয়। প্রতি আসরে আমরা আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করেছি, সাফ গেমসের সব চাইতে আকর্ষনীয় এবং মর্যাদাপূর্ণ ইভেন্টটিতে নিশ্চয় আমাদের ফুটবলাররা অতীতের ব্যর্থতাকে ঢেকে দিয়ে ছিনিয়ে আনবে সোনার পদক। কিন্তু মাঠে আমাদের সে স্বপ্ন মুখ থুবড়ে পড়েছে। তবে ২০০৩ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৩য় সাফ ফুটবলে আমরা শিরোপা জয় করেছি, তবে আগের দুটো আসরে বুক ভেঙ্গে গেছে দলের বর্থ্যতায়। ৩য় সাফ ফুটবলে শিরোপা জয়ের পরই আবার একই বছর ইসলামাবাদ সাফ গেমস ফুটবলে আমাদের ফলাফল ছিলো লজ্জাজনক। আসলে ফুটবল পাগল জাতি হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ফুটবলে আমাদের অবস্থান আজও দুঃখজনকভাবে অনেক পেছনে। সদ্যসমাপ্ত সাফ গেমসের পরিবর্তিত রূপ এসএ গেমস, শ্রীলঙ্কা ২০০৬-এ বাংলাদেশ ফুটবল দলের ব্যর্থতা জাতিকে আবারো হতাশার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। গেমসে বাংলাদেশের নাম ফেভারিট হিসেবে উচ্চারিত হলেও, বাংলাদেশ দল প্রথম রাউন্ডের গণ্ডি পেরুতে পারে নি। মোট কথা, বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব থেকে শুরু করে, এশিয়ান ফুটবলে আমাদের জাতীয় দলের ফলাফল মোটেও সুখপ্রদ নয়। আজ ভারত, পাকিস্তান তো দূরের কথা,- নেপাল, মালদ্বীপের মতো দেশের ফুটবলও আমাদের চাইতে অনেক এগিয়ে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ছিটেফোটা সাফল্য থাকলেও ব্যর্থতার বোঝাটা বেশী ভারী। এছাড়া বিভিন্ন সময় আমাদের দেশের ক্লাবগুলো দেশ-বিদেশের মাঠে নৈপুণ্য প্রদর্শন করে তুলে এনেছে সাফল্য।
সত্তর-আশির দশকে ঢাকার ফুটবল সবসময়ই সরগরম থাকতো। আগা খান গোল্ড কাপকে ঘিরে বসতো জমজমাট আন্তর্জাতিক ফুটবল। প্রেসিডেন্ট গোল্ড কাপের আন্তর্জাতিক ফুটবল উৎসবে মেতে উঠতো ফুটবলামোদীরা। উল্লেখ্য, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট গোল্ডকাপের শিরোপা জয় করেছিলো বাংলাদেশ আর সেটাই আন্তর্জাতিক ফুটবলে আমাদের অর্জিত প্রথম ট্রফি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশের অবস্থান মোটেও ভালো নয়। আগের সাতটি আসরে নাকানি-চুবানি খেয়ে, বছরের পর বছর অপেক্ষা করে ১৯৯৯ সালে কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত অষ্টম সাফ গেমস ফুটবলে সোনা পেয়েছে বাংলাদেশ। তবে ঐ একবারই। এরপর আর নয়। প্রতি আসরে আমরা আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করেছি, সাফ গেমসের সব চাইতে আকর্ষনীয় এবং মর্যাদাপূর্ণ ইভেন্টটিতে নিশ্চয় আমাদের ফুটবলাররা অতীতের ব্যর্থতাকে ঢেকে দিয়ে ছিনিয়ে আনবে সোনার পদক। কিন্তু মাঠে আমাদের সে স্বপ্ন মুখ থুবড়ে পড়েছে। তবে ২০০৩ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৩য় সাফ ফুটবলে আমরা শিরোপা জয় করেছি, তবে আগের দুটো আসরে বুক ভেঙ্গে গেছে দলের বর্থ্যতায়। ৩য় সাফ ফুটবলে শিরোপা জয়ের পরই আবার একই বছর ইসলামাবাদ সাফ গেমস ফুটবলে আমাদের ফলাফল ছিলো লজ্জাজনক। আসলে ফুটবল পাগল জাতি হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ফুটবলে আমাদের অবস্থান আজও দুঃখজনকভাবে অনেক পেছনে। সদ্যসমাপ্ত সাফ গেমসের পরিবর্তিত রূপ এসএ গেমস, শ্রীলঙ্কা ২০০৬-এ বাংলাদেশ ফুটবল দলের ব্যর্থতা জাতিকে আবারো হতাশার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। গেমসে বাংলাদেশের নাম ফেভারিট হিসেবে উচ্চারিত হলেও, বাংলাদেশ দল প্রথম রাউন্ডের গণ্ডি পেরুতে পারে নি। মোট কথা, বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব থেকে শুরু করে, এশিয়ান ফুটবলে আমাদের জাতীয় দলের ফলাফল মোটেও সুখপ্রদ নয়। আজ ভারত, পাকিস্তান তো দূরের কথা,- নেপাল, মালদ্বীপের মতো দেশের ফুটবলও আমাদের চাইতে অনেক এগিয়ে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ছিটেফোটা সাফল্য থাকলেও ব্যর্থতার বোঝাটা বেশী ভারী। এছাড়া বিভিন্ন সময় আমাদের দেশের ক্লাবগুলো দেশ-বিদেশের মাঠে নৈপুণ্য প্রদর্শন করে তুলে এনেছে সাফল্য।
স্বা ধী ন তা র প র ঢা কা র ফু ট ব লে সে রা রা
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) স্বাধীনতার পর অনেক প্রতিভাধর খেলোযাড়ের আবির্ভাব ঘটেছে ঢাকার ফুটবলে। এদের মধ্যে সেরা কিছু খেলোয়াড়ের নাম তুলে ধরা হলো- সালাহউদ্দিন, আশিষ ভদ্র, টিপু, নওশের, জহির, পিন্টু, আমিন, মঞ্জু, মেজর হাফিজ, এনায়েত, রামা, আবুল, অমলেস, মোহসীন, সামসু, কানন, সালাম মুর্শেদী, বাদল রায়, কায়সার, সাব্বির, আয়াজ, মিজান, জনি, এমিলি, সাদেক, নান্নু, টুটুল, চুন্নু, জামিল, আকতার, ইফসুফ, এফআই কামাল,রুপু, রনজিৎ আসলাম, রুমি, মুন্না, মামুন, রেহান, আলমগীর, মোতালিব, কাল, সামসু, শফিকুল ইসলাম মানিক, কানন, বাবলু, লাবলু, ওয়াসিম, আজমত, হালিম, সিজার, রকিব, ইশবাল, মানিক-১, মুন, বাদল দাস, জোসী, মাসুদ, তুহিন, টিটো, মর্তজা, বাটু, আবুল, খুরশিদ বাবুল, বাবুল, মনু, উত্তম, বাবুল, পনির, পিযুস, গিয়াস, আমান, রুবেল প্রমূখ। সাম্প্রতিক সময়ে আরো অনেক ফুটবলার তাদের নৈপুণ্য দিয়ে দর্শকদের নজর কেড়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- জুয়েল রানা, নকিব, আলফাজ, মাসুদ রানা, জয় প্রমুখ।
স্বাধীনতার পর অনেক প্রতিভাধর খেলোযাড়ের আবির্ভাব ঘটেছে ঢাকার ফুটবলে। এদের মধ্যে সেরা কিছু খেলোয়াড়ের নাম তুলে ধরা হলো- সালাহউদ্দিন, আশিষ ভদ্র, টিপু, নওশের, জহির, পিন্টু, আমিন, মঞ্জু, মেজর হাফিজ, এনায়েত, রামা, আবুল, অমলেস, মোহসীন, সামসু, কানন, সালাম মুর্শেদী, বাদল রায়, কায়সার, সাব্বির, আয়াজ, মিজান, জনি, এমিলি, সাদেক, নান্নু, টুটুল, চুন্নু, জামিল, আকতার, ইফসুফ, এফআই কামাল,রুপু, রনজিৎ আসলাম, রুমি, মুন্না, মামুন, রেহান, আলমগীর, মোতালিব, কাল, সামসু, শফিকুল ইসলাম মানিক, কানন, বাবলু, লাবলু, ওয়াসিম, আজমত, হালিম, সিজার, রকিব, ইশবাল, মানিক-১, মুন, বাদল দাস, জোসী, মাসুদ, তুহিন, টিটো, মর্তজা, বাটু, আবুল, খুরশিদ বাবুল, বাবুল, মনু, উত্তম, বাবুল, পনির, পিযুস, গিয়াস, আমান, রুবেল প্রমূখ। সাম্প্রতিক সময়ে আরো অনেক ফুটবলার তাদের নৈপুণ্য দিয়ে দর্শকদের নজর কেড়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- জুয়েল রানা, নকিব, আলফাজ, মাসুদ রানা, জয় প্রমুখ।
ফু ট ব লা র দে র পা রি শ্র মি ক
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) স্বাধীনতার পর দেশের ফুটবলের উত্তরণের সাথে সাথে বাড়তে থাকে ফুটবলারদের পারিশ্রমিক। বিশেষ করে আশির দশকে এই পারিশ্রমিকের পরিমাণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে স্টার, সুপারস্টার ফুটবলারদের পারিশ্রমিক দশ থেকে বিশ লাখ পর্যন্ত ওঠানামা করেছে। ’৮৬ থেকে ’৮৯ পর্যন্ত সাড়া জাগানো ডিফেন্ডার কায়সার হামিদ ছিলেন সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত খেলোয়াড়। এ সময় তার পারিশ্রমিক ১০ থেকে ১৩/১৪ লাখে ওঠানামা করেছে। আসলাম, সাব্বির , মোনেম মুন্না, রুমি, জুয়েল রানা, নকিবের মতো খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক ১০ লাখের ওপরে ছিলো। তবে নব্বই দশকের একেবারে গোড়ায় বিস্ফোরণ ঘটান মোনেম মুন্না। এ সময় তিনি আবাহনীর নিকট থেকে ২০ লাখ টাকা পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন। এদেশের ফুটবল ইতিহাসে যা একটা রেকর্ড। কিন্তু দুঃখজনক সত্যি হচ্ছে, ফুটবলের গতি মন্থর হওয়ার সাথে সাথে ফুটবলারদের পারিশ্রমিক কমতে থাকে। মাঝখানে ফুটবলারদের পারিশ্রমিক তো আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছিলো, কিন্তু বর্তমানে তা কিছুটা বেড়েছে। আশি-নব্বইয়ের দশকে যেখানে ফুটবলারদের পারিশ্রমিক ১০ লাখ থেকে ২০ লাখ টাকায় ওঠানামা করেছে, সে ধারাবাহিকতায় ২০০৪-৫ সালে ফুটবলারদের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক বেড়ে ৩০/৩৫ লাখ টাকা হওয়ার কথা- কিন্তু তা হয়নি; বরং কমে গেছে অনেক।
স্বাধীনতার পর দেশের ফুটবলের উত্তরণের সাথে সাথে বাড়তে থাকে ফুটবলারদের পারিশ্রমিক। বিশেষ করে আশির দশকে এই পারিশ্রমিকের পরিমাণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে স্টার, সুপারস্টার ফুটবলারদের পারিশ্রমিক দশ থেকে বিশ লাখ পর্যন্ত ওঠানামা করেছে। ’৮৬ থেকে ’৮৯ পর্যন্ত সাড়া জাগানো ডিফেন্ডার কায়সার হামিদ ছিলেন সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত খেলোয়াড়। এ সময় তার পারিশ্রমিক ১০ থেকে ১৩/১৪ লাখে ওঠানামা করেছে। আসলাম, সাব্বির , মোনেম মুন্না, রুমি, জুয়েল রানা, নকিবের মতো খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক ১০ লাখের ওপরে ছিলো। তবে নব্বই দশকের একেবারে গোড়ায় বিস্ফোরণ ঘটান মোনেম মুন্না। এ সময় তিনি আবাহনীর নিকট থেকে ২০ লাখ টাকা পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন। এদেশের ফুটবল ইতিহাসে যা একটা রেকর্ড। কিন্তু দুঃখজনক সত্যি হচ্ছে, ফুটবলের গতি মন্থর হওয়ার সাথে সাথে ফুটবলারদের পারিশ্রমিক কমতে থাকে। মাঝখানে ফুটবলারদের পারিশ্রমিক তো আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছিলো, কিন্তু বর্তমানে তা কিছুটা বেড়েছে। আশি-নব্বইয়ের দশকে যেখানে ফুটবলারদের পারিশ্রমিক ১০ লাখ থেকে ২০ লাখ টাকায় ওঠানামা করেছে, সে ধারাবাহিকতায় ২০০৪-৫ সালে ফুটবলারদের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক বেড়ে ৩০/৩৫ লাখ টাকা হওয়ার কথা- কিন্তু তা হয়নি; বরং কমে গেছে অনেক।
কা লো টা কা র দা প ট
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) কারো কারো মতে, আশির দশকের শেষদিকে ফুটবলে কালো টাকার দাপট বেড়ে যায়, যা ফুটবলের ক্ষতির পেছনে আর একটি বড় কারণ। সে সময় যাচ্ছেতাইভাবে কালো টাকার ছড়াছড়ি ফুটবলারদের বিভ্রান্ত করে ফেলেছিলো। ফলে তারা নিজেদের খেলার মানের দিকে যতোনা মনোযোগী হয়েছে, তার চাইতে বেশী ছুটেছে টাকার পেছনে। আর এদের অনুসরণ করেছে পরের জেনারেশন। তখন বড় দলগুলো যেনো টাকার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেছিলো। একটু নজর কেড়েছে এমন খেলোযাড়কেও তারা সে সময় ৫/৬ লাখ টাকায় চুক্তি করেছেন। এ সময় রসিকজনেরা বলতেন- ‘বুটের ফিতে বাঁধতে জানলেই ঢাকার মাঠে পাঁচ-সাত লাখ টাকা আয় করা যায়।’ বড় দলগুলোর সাথে ছোট দলগুলোর, বড় মাপের খেলোয়াড়দের সাথে ছোটমাপের খেলোয়াড়দের অর্থনৈতিক বিশাল বৈষম্যও ফুটবলের অনেক ক্ষতি সাধন করেছে। মানসম্পন্ন ফুটবলার তৈরীর ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে প্রতিবন্ধকতা। ১৯৯১ সালে এক সাক্ষাৎকারে ’৭৮ সালে ইরানের হয়ে বিশ্বকাপে অংশ নেয়া খেলোয়াড় এবং ঢাকা মোহামেডান ও বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী নাসের হেজাজী বলেছিলেন, ‘ফুটবলারদের মানের চাইতে পারিশ্রমিক বাড়াটা ফুটবলের জন্য ক্ষতিকর। অধিক পারিশ্রমিক খেলার মানোন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।’
কারো কারো মতে, আশির দশকের শেষদিকে ফুটবলে কালো টাকার দাপট বেড়ে যায়, যা ফুটবলের ক্ষতির পেছনে আর একটি বড় কারণ। সে সময় যাচ্ছেতাইভাবে কালো টাকার ছড়াছড়ি ফুটবলারদের বিভ্রান্ত করে ফেলেছিলো। ফলে তারা নিজেদের খেলার মানের দিকে যতোনা মনোযোগী হয়েছে, তার চাইতে বেশী ছুটেছে টাকার পেছনে। আর এদের অনুসরণ করেছে পরের জেনারেশন। তখন বড় দলগুলো যেনো টাকার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেছিলো। একটু নজর কেড়েছে এমন খেলোযাড়কেও তারা সে সময় ৫/৬ লাখ টাকায় চুক্তি করেছেন। এ সময় রসিকজনেরা বলতেন- ‘বুটের ফিতে বাঁধতে জানলেই ঢাকার মাঠে পাঁচ-সাত লাখ টাকা আয় করা যায়।’ বড় দলগুলোর সাথে ছোট দলগুলোর, বড় মাপের খেলোয়াড়দের সাথে ছোটমাপের খেলোয়াড়দের অর্থনৈতিক বিশাল বৈষম্যও ফুটবলের অনেক ক্ষতি সাধন করেছে। মানসম্পন্ন ফুটবলার তৈরীর ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে প্রতিবন্ধকতা। ১৯৯১ সালে এক সাক্ষাৎকারে ’৭৮ সালে ইরানের হয়ে বিশ্বকাপে অংশ নেয়া খেলোয়াড় এবং ঢাকা মোহামেডান ও বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী নাসের হেজাজী বলেছিলেন, ‘ফুটবলারদের মানের চাইতে পারিশ্রমিক বাড়াটা ফুটবলের জন্য ক্ষতিকর। অধিক পারিশ্রমিক খেলার মানোন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।’
পা তা নো খে লা
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) ফুটবলে অর্থের দাপট বাড়ার সাথে সাথে পাতানো খেলার প্রভাব বাড়তে থাকে। শিরোপাকে করায়ত্ত করার জন্য বড় দলগুলো মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে পাতানো খেলা খেলতে শুরু করে। আবার রেলিগেশনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছোট দলগুলো অর্থের বিনিময়ে পাতানো খেলার সুযোগ নিতে থাকে। আর এই পাতানো খেলার কালচার ফুটবলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। পাশাপাশি দর্শকরা হতে থাকে প্রতারিত। ফুটবলের মান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার এটি আর একটি কারণ। ঢাকার মাঠে এখনো পাতানো খেলা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একজন সাবেক খেলোয়াড়ের ভাষ্য হচ্ছে, ‘ফুটবলে এখন পাতানো খেলা আশঙ্কাজনক রূপ নিয়েছে।’ এ প্রসঙ্গে তিনি জাতীয় ফুটবল ২০০৫-এর কয়েকটি খেলার উদাহরণ দেন।
ফুটবলে অর্থের দাপট বাড়ার সাথে সাথে পাতানো খেলার প্রভাব বাড়তে থাকে। শিরোপাকে করায়ত্ত করার জন্য বড় দলগুলো মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে পাতানো খেলা খেলতে শুরু করে। আবার রেলিগেশনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছোট দলগুলো অর্থের বিনিময়ে পাতানো খেলার সুযোগ নিতে থাকে। আর এই পাতানো খেলার কালচার ফুটবলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। পাশাপাশি দর্শকরা হতে থাকে প্রতারিত। ফুটবলের মান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার এটি আর একটি কারণ। ঢাকার মাঠে এখনো পাতানো খেলা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একজন সাবেক খেলোয়াড়ের ভাষ্য হচ্ছে, ‘ফুটবলে এখন পাতানো খেলা আশঙ্কাজনক রূপ নিয়েছে।’ এ প্রসঙ্গে তিনি জাতীয় ফুটবল ২০০৫-এর কয়েকটি খেলার উদাহরণ দেন।
বি দে শী খে লো য়া ড়
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) ঢাকার মাঠে বিদেশী খেলোয়াড়ের আসা-যাওয়া অনেক আগে থেকেই ছিলো। । পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ঢাকার ফুটবলে মারকানী ও বেলুচিস্তানের ফুটবলারদের দাপট ছিলো বেশ। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে উপমহাদেশের অনেক খ্যাতিমান খেলোয়াড় ঢাকায় খেলে গেছেন। সে সময় ওয়ারী, ভিক্টোরিয়া, ওয়ান্ডারার্স, ইপিআইডিসিতে পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারী ও পাঞ্জাবী খেলোয়াড়দের আসা-যাওয়া ছিলো লক্ষ্যণীয়। স্বাধীন দেশের মাটিতে প্রথম বিদেশী খেলোয়াড় নিয়ে আসে মোহামেডান। ১৯৭৪ সালে ভারতের চন্দ্রশেখর প্রসাদ ও প্রভাকর মিশ্র মোহামেডানের পক্ষে খেলতে ঢাকায় আসেন। মাঝখানে বিরতির পর ১৯৭৭ সালে আবার ঢাকায় বিদেশী খেলোয়াড়ের আবির্ভাব ঘটে। এ বছর মোহামেডানে পাকিস্তানের কালা গফুর, আশিক আলী, ফজলুর রহমান ও আফজাল হোসেন খেলেন এবং আবাহনীতে খেলেন শ্রীলঙ্কার গোলরক্ষক লায়নেল পিরিচ ও স্ট্রাইকার মহেন্দ্র পালা। আর এই দুই শ্রীলঙ্কান ফুটবলারের কল্যাণেই সেবার আবাহনী লীগ শিরোপা ঘরে তুলতে সক্ষম হয়। ১৯৭৮ সালেও আবাহনীতে লায়নেল পিরিচ ও মহেন্দ্র পালা খেলেন। এ বছর মোহামেডানের পক্ষে নেপালের সাক্য বড়ুয়া, এবং রহমতগঞ্জের পক্ষে স্কটিশ ফুটবলার পলকাসিং খেলেন। ১৯৭৯ সালে মোহামেডান ও ওয়ারীতে দু’জন করে ভারতীয় ও রহমতগঞ্জে নাইজেরিয়ান খেলোয়াড় টম খেলেন। ১৯৮০ সালে ভুটানের বাসনাত মোহামেডানের পক্ষে খেলেন। এরপর থেকে ঢাকার ফুটবলে বিদেশী খেলোয়াড়ের সংখ্যা বেড়ে যায়। আশি ও নব্বইয়ের দশকে ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, নাইজেরিয়া, ব্রাজিল, হল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, থাইল্যান্ড, ঘানা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের বেশ কিছু সংখ্যক খেলোয়াড় ঢাকায় খেলেন। তবে এ ক্ষেত্রে একটি ব্যাপার লক্ষনীয় আর তা হচ্ছে, প্রথম দিকে মানসম্পন্ন বিদেশী খেলোয়াড়ের আবির্ভাব ঘটলেও দিন যতোই যেতে থাকে দেশীয় ফুটবল এবং ফুটবলারদের সাথে পাল্লা দিয়ে বিদেশী ফুটবলারের মানও ততোই কমতে থাকে। ক্লাবগুলো ‘মান’ নয় ‘বিদেশী’ শব্দটাকেই অধিক গুরুত্ব দিতে থাকে। অনেকের মতে, স্রোতের মতো আসা এই সব বিদেশী খেলোয়াড় দেশের ফুটবলে যতোটা না কল্যাণ বয়ে আনছে, তার চাইতে ক্ষতিই করছে বেশী। এদের জন্য প্রতিভাধর অনেক দেশীয় ফুটবলারকে সাইড লাইনে বসে থাকতে হচ্ছে। একসময় যেমন বিদেশী ফুটবলাররা আমাদের ফুটবলের মান এবং সৌন্দর্য-দু’টোই বাড়াতো। বেশ উঁচু-মানের সেই সব খেলোয়াড়ের নাম এখনো ফুটবল প্রেমিকদের মুখে শোনা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শ্রীলঙ্কার পাকির আলী, লায়নেল পিরিচ, প্রেমলাল, চন্দ্রসিড়ি, অশোকা, নেপালের গনেশ থাপা, কৃষ্ণ থাপা, মান বাহাদুর থাপা, গালে, ভুটানের খরগ বাহাদুর বাসনাত, পাকিস্তানের কালা গফুর, নাইজেরিয়ার ইব্রাহিম সেঙ্গার, চিমা ওকেরী, এমেকা ইউজি, ইরানের নাসের হেজাজী (কোচ কাম গোল রক্ষক), নালজেগার, মর্তুজা, বোরহান জাগেদ, ভিজেন তাহেরী, ইরাকের শামির শাকির, করিম মোহাম্মদ, রাশিয়ার সের্গেই ঝুকভ, কাজাকভ আন্দ্রে, উজবেকিস্তানের আব্দুর রহিমভ। ১৯৮১ সালে আবাহনীতে খেলতে আসা শ্রীলঙ্কার ডিফেন্ডার পাকির আলীী পরবর্তীতে দীর্ঘ আট বছর আবাহনীর জার্সি গায়ে চাপিয়ে নিজের চমৎকার ফুটবল নৈপুণ্য প্রদর্শন করে এদেশের ফুটবলানুরাগীদের মন জয় করে নেন। বলতে গেলে, তিনি যেনো এদেশের মাটি ও মানুষের সাথে মিশেই গিয়েছিলেন। ’৮৩, ’৮৪ ও ’৮৫ সালে পরপর তিনবার লীগের শিরোপা অর্জন করে আবাহনী যে দুর্লভ হ্যাট্রিক করে তার পেছনে পাকির আলীর ছিলো অসামান্য অবদান। একথা সে সময়ের দর্শক এবং ফুটবলবোদ্ধারা অকপটে স্বীকার করতেন যে, পাকির আলী যতোদিন আবাহনীতে ছিলেন আবাহনীর রক্ষণভাগকে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ বানিয়ে রেখেছিলেন । সর্বশেষ তিনি ’৯১-৯২ তে পিডব্লিউডিতে খেলেন। টানা চার বছর আবাহনীর জার্সি গায়ে চাপিয়ে খেলেন শ্রীলঙ্কার স্ট্রাইকার প্রেমলাল। তিনিও সর্বশষ ’৯১-৯২ তে পিডব্লিউডিতে খেলেন। শ্রীলঙ্কার অশোকা টানা পাঁচ বছর খেলেন আবাহনীতে। নেপালের গনেশ থাপা টানা চার বছর ঢাকা লীগে খেলেন। এখনো প্রতি বছর ঢাকা মাঠে খেলছেন অনেক বিদেশী খেলোয়াড়, কিন্তু তাদের কেউই পাকির আলীদের মতো মানসম্পন্ন ফুটবল নৈপুণ্য উপহার দিয়ে ফুটবল দর্শকদের মনে স্থান করে নিতে পারছেন না। এ সম্পর্কে সমালোচকদের ভাষ্য হচ্ছে, যাদের মান-ই নেই তারা মাঠ-ই মাতাবে কি, আর দর্শকদের নজরই বা কাড়বে কি।
ঢাকার মাঠে বিদেশী খেলোয়াড়ের আসা-যাওয়া অনেক আগে থেকেই ছিলো। । পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ঢাকার ফুটবলে মারকানী ও বেলুচিস্তানের ফুটবলারদের দাপট ছিলো বেশ। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে উপমহাদেশের অনেক খ্যাতিমান খেলোয়াড় ঢাকায় খেলে গেছেন। সে সময় ওয়ারী, ভিক্টোরিয়া, ওয়ান্ডারার্স, ইপিআইডিসিতে পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারী ও পাঞ্জাবী খেলোয়াড়দের আসা-যাওয়া ছিলো লক্ষ্যণীয়। স্বাধীন দেশের মাটিতে প্রথম বিদেশী খেলোয়াড় নিয়ে আসে মোহামেডান। ১৯৭৪ সালে ভারতের চন্দ্রশেখর প্রসাদ ও প্রভাকর মিশ্র মোহামেডানের পক্ষে খেলতে ঢাকায় আসেন। মাঝখানে বিরতির পর ১৯৭৭ সালে আবার ঢাকায় বিদেশী খেলোয়াড়ের আবির্ভাব ঘটে। এ বছর মোহামেডানে পাকিস্তানের কালা গফুর, আশিক আলী, ফজলুর রহমান ও আফজাল হোসেন খেলেন এবং আবাহনীতে খেলেন শ্রীলঙ্কার গোলরক্ষক লায়নেল পিরিচ ও স্ট্রাইকার মহেন্দ্র পালা। আর এই দুই শ্রীলঙ্কান ফুটবলারের কল্যাণেই সেবার আবাহনী লীগ শিরোপা ঘরে তুলতে সক্ষম হয়। ১৯৭৮ সালেও আবাহনীতে লায়নেল পিরিচ ও মহেন্দ্র পালা খেলেন। এ বছর মোহামেডানের পক্ষে নেপালের সাক্য বড়ুয়া, এবং রহমতগঞ্জের পক্ষে স্কটিশ ফুটবলার পলকাসিং খেলেন। ১৯৭৯ সালে মোহামেডান ও ওয়ারীতে দু’জন করে ভারতীয় ও রহমতগঞ্জে নাইজেরিয়ান খেলোয়াড় টম খেলেন। ১৯৮০ সালে ভুটানের বাসনাত মোহামেডানের পক্ষে খেলেন। এরপর থেকে ঢাকার ফুটবলে বিদেশী খেলোয়াড়ের সংখ্যা বেড়ে যায়। আশি ও নব্বইয়ের দশকে ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, নাইজেরিয়া, ব্রাজিল, হল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, থাইল্যান্ড, ঘানা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের বেশ কিছু সংখ্যক খেলোয়াড় ঢাকায় খেলেন। তবে এ ক্ষেত্রে একটি ব্যাপার লক্ষনীয় আর তা হচ্ছে, প্রথম দিকে মানসম্পন্ন বিদেশী খেলোয়াড়ের আবির্ভাব ঘটলেও দিন যতোই যেতে থাকে দেশীয় ফুটবল এবং ফুটবলারদের সাথে পাল্লা দিয়ে বিদেশী ফুটবলারের মানও ততোই কমতে থাকে। ক্লাবগুলো ‘মান’ নয় ‘বিদেশী’ শব্দটাকেই অধিক গুরুত্ব দিতে থাকে। অনেকের মতে, স্রোতের মতো আসা এই সব বিদেশী খেলোয়াড় দেশের ফুটবলে যতোটা না কল্যাণ বয়ে আনছে, তার চাইতে ক্ষতিই করছে বেশী। এদের জন্য প্রতিভাধর অনেক দেশীয় ফুটবলারকে সাইড লাইনে বসে থাকতে হচ্ছে। একসময় যেমন বিদেশী ফুটবলাররা আমাদের ফুটবলের মান এবং সৌন্দর্য-দু’টোই বাড়াতো। বেশ উঁচু-মানের সেই সব খেলোয়াড়ের নাম এখনো ফুটবল প্রেমিকদের মুখে শোনা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শ্রীলঙ্কার পাকির আলী, লায়নেল পিরিচ, প্রেমলাল, চন্দ্রসিড়ি, অশোকা, নেপালের গনেশ থাপা, কৃষ্ণ থাপা, মান বাহাদুর থাপা, গালে, ভুটানের খরগ বাহাদুর বাসনাত, পাকিস্তানের কালা গফুর, নাইজেরিয়ার ইব্রাহিম সেঙ্গার, চিমা ওকেরী, এমেকা ইউজি, ইরানের নাসের হেজাজী (কোচ কাম গোল রক্ষক), নালজেগার, মর্তুজা, বোরহান জাগেদ, ভিজেন তাহেরী, ইরাকের শামির শাকির, করিম মোহাম্মদ, রাশিয়ার সের্গেই ঝুকভ, কাজাকভ আন্দ্রে, উজবেকিস্তানের আব্দুর রহিমভ। ১৯৮১ সালে আবাহনীতে খেলতে আসা শ্রীলঙ্কার ডিফেন্ডার পাকির আলীী পরবর্তীতে দীর্ঘ আট বছর আবাহনীর জার্সি গায়ে চাপিয়ে নিজের চমৎকার ফুটবল নৈপুণ্য প্রদর্শন করে এদেশের ফুটবলানুরাগীদের মন জয় করে নেন। বলতে গেলে, তিনি যেনো এদেশের মাটি ও মানুষের সাথে মিশেই গিয়েছিলেন। ’৮৩, ’৮৪ ও ’৮৫ সালে পরপর তিনবার লীগের শিরোপা অর্জন করে আবাহনী যে দুর্লভ হ্যাট্রিক করে তার পেছনে পাকির আলীর ছিলো অসামান্য অবদান। একথা সে সময়ের দর্শক এবং ফুটবলবোদ্ধারা অকপটে স্বীকার করতেন যে, পাকির আলী যতোদিন আবাহনীতে ছিলেন আবাহনীর রক্ষণভাগকে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ বানিয়ে রেখেছিলেন । সর্বশেষ তিনি ’৯১-৯২ তে পিডব্লিউডিতে খেলেন। টানা চার বছর আবাহনীর জার্সি গায়ে চাপিয়ে খেলেন শ্রীলঙ্কার স্ট্রাইকার প্রেমলাল। তিনিও সর্বশষ ’৯১-৯২ তে পিডব্লিউডিতে খেলেন। শ্রীলঙ্কার অশোকা টানা পাঁচ বছর খেলেন আবাহনীতে। নেপালের গনেশ থাপা টানা চার বছর ঢাকা লীগে খেলেন। এখনো প্রতি বছর ঢাকা মাঠে খেলছেন অনেক বিদেশী খেলোয়াড়, কিন্তু তাদের কেউই পাকির আলীদের মতো মানসম্পন্ন ফুটবল নৈপুণ্য উপহার দিয়ে ফুটবল দর্শকদের মনে স্থান করে নিতে পারছেন না। এ সম্পর্কে সমালোচকদের ভাষ্য হচ্ছে, যাদের মান-ই নেই তারা মাঠ-ই মাতাবে কি, আর দর্শকদের নজরই বা কাড়বে কি।
শে ষ ক থা
![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=150&h=101) ঢাকার ফুটবলের সাথে সারা দেশের ফুটবলের উত্থান-পতনের রয়েছে একটা সুগভীর সম্পর্ক। ঢাকার ফুটবলকে সামনে রেখেই গড়ে ওঠে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ফুটবলাররা। আজ ঢাকার ফুটবল নানা অনিয়ম, অব্যবস্থা আর দুর্নীতির মধ্যে নিপতিত। নেই সেই অকৃত্রিম ফুটবলপ্রীতি খেলোয়াড় ও সংগঠকদের মাঝে। বরং দুঃখজনকভাবে বেড়েছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। ফেডারেশনে চলে গেছে ক্ষমতাসীনদের দখলে। সেখানেও দলাদলি। ফুটবলকে রাখতে হবে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত। একথা তো কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না যে, ফুটবল বাঁচলে এদেশের খেলাধুলা বাঁচবে। আর খেলাধুলা বাঁচলে দেশ সুস্থ এবং শক্ত-সমর্থ প্রজন্ম পাবে। কমে যাবে অপরাধীর সংখ্যা আর অপরাধপ্রবণতা। কাজেই অত্যন্ত সহজলভ্য আর সেরা আনন্দদায়ক ফুটবলটাকে আজ আগে বাঁচানো জরুরী। ফুটবলের আঙ্গিনায় বিরাজিত কালবেলাকে মুছে দিয়ে আলোর ঝলকানি আনতে সকলকে হতে হবে সোচ্চার।
ঢাকার ফুটবলের সাথে সারা দেশের ফুটবলের উত্থান-পতনের রয়েছে একটা সুগভীর সম্পর্ক। ঢাকার ফুটবলকে সামনে রেখেই গড়ে ওঠে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ফুটবলাররা। আজ ঢাকার ফুটবল নানা অনিয়ম, অব্যবস্থা আর দুর্নীতির মধ্যে নিপতিত। নেই সেই অকৃত্রিম ফুটবলপ্রীতি খেলোয়াড় ও সংগঠকদের মাঝে। বরং দুঃখজনকভাবে বেড়েছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। ফেডারেশনে চলে গেছে ক্ষমতাসীনদের দখলে। সেখানেও দলাদলি। ফুটবলকে রাখতে হবে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত। একথা তো কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না যে, ফুটবল বাঁচলে এদেশের খেলাধুলা বাঁচবে। আর খেলাধুলা বাঁচলে দেশ সুস্থ এবং শক্ত-সমর্থ প্রজন্ম পাবে। কমে যাবে অপরাধীর সংখ্যা আর অপরাধপ্রবণতা। কাজেই অত্যন্ত সহজলভ্য আর সেরা আনন্দদায়ক ফুটবলটাকে আজ আগে বাঁচানো জরুরী। ফুটবলের আঙ্গিনায় বিরাজিত কালবেলাকে মুছে দিয়ে আলোর ঝলকানি আনতে সকলকে হতে হবে সোচ্চার।
Filed under: Uncategorized | Leave a comment »




 মাহাবুবুল হাসান নীরুর ই-গ্রন্থ 'সেরা দশ গল্প'। অসাধারণ দশটি গল্পের এক অনবদ্য উপস্থাপন। বইটি পড়তে ক্লিক করুন
মাহাবুবুল হাসান নীরুর ই-গ্রন্থ 'সেরা দশ গল্প'। অসাধারণ দশটি গল্পের এক অনবদ্য উপস্থাপন। বইটি পড়তে ক্লিক করুন ছবি ফেলে আসা এবং চলমান সময়ের কথা বলে। ধরে রাখে সময়কে স্মৃদির ফ্রেমে। মাহাবুবুল হাসান নীরু অ্যালবামটি দেখতে ক্লিক করুন
ছবি ফেলে আসা এবং চলমান সময়ের কথা বলে। ধরে রাখে সময়কে স্মৃদির ফ্রেমে। মাহাবুবুল হাসান নীরু অ্যালবামটি দেখতে ক্লিক করুন মাহাবুবুল হাসান নীরুর ই-গ্রন্থ 'হৃদয়ছোঁয়া পঁয়ত্রিশ'। দৃষ্টিনন্দন অলঙ্করণ আর মন-জমিনে দাগ কাটার মতো পঁয়ত্রিশটি ছড়া-কাব্য। বইটি পড়তে ক্লিক করুন
মাহাবুবুল হাসান নীরুর ই-গ্রন্থ 'হৃদয়ছোঁয়া পঁয়ত্রিশ'। দৃষ্টিনন্দন অলঙ্করণ আর মন-জমিনে দাগ কাটার মতো পঁয়ত্রিশটি ছড়া-কাব্য। বইটি পড়তে ক্লিক করুন মাহাবুবুল হাসান নীরুর খেলাধুলা বিষয়ক লেখা পড়ার জন্য ক্লিক করুন
মাহাবুবুল হাসান নীরুর খেলাধুলা বিষয়ক লেখা পড়ার জন্য ক্লিক করুন মাহাবুবুল হাসান নীরুর শিশুতোষ লেখাগুলো পড়তে ক্লিক করুন
মাহাবুবুল হাসান নীরুর শিশুতোষ লেখাগুলো পড়তে ক্লিক করুন মাহাবুবুল হাসান নীরুর গল্প পড়তে ক্লিক করুন
মাহাবুবুল হাসান নীরুর গল্প পড়তে ক্লিক করুন মাহাবুবুল হাসান নীরুর ছড়া পড়তে ক্লিক করুন
মাহাবুবুল হাসান নীরুর ছড়া পড়তে ক্লিক করুন![foota24[1]](https://mahaneebas.files.wordpress.com/2013/07/foota2411.png?w=468&h=315)

 মাহাবুবুল হাসান নীরুর ই-গ্রন্থ 'হৃদয়ছোঁয়া পঁয়ত্রিশ'। দৃষ্টিনন্দন অলঙ্করণ আর মন-জমিনে দাগ কাটার মতো পঁয়ত্রিশটি ছড়া-কাব্য। বইটি পড়তে ক্লিক করুন.....
মাহাবুবুল হাসান নীরুর ই-গ্রন্থ 'হৃদয়ছোঁয়া পঁয়ত্রিশ'। দৃষ্টিনন্দন অলঙ্করণ আর মন-জমিনে দাগ কাটার মতো পঁয়ত্রিশটি ছড়া-কাব্য। বইটি পড়তে ক্লিক করুন..... youtube-এর mhniru's channel-এ মাহাবুবুল হাসান নীরুর নাটক, টক-শো দেখতে ক্লিক করুন.....
youtube-এর mhniru's channel-এ মাহাবুবুল হাসান নীরুর নাটক, টক-শো দেখতে ক্লিক করুন..... গুগল বাংলায় মাহাবুবুল হাসান নীরুর বই, ভিডিও ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে, এবং তার লেখা পড়তে ক্লিক করুন
গুগল বাংলায় মাহাবুবুল হাসান নীরুর বই, ভিডিও ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে, এবং তার লেখা পড়তে ক্লিক করুন ফেসবুকে মাহাবুবুল হাসান নীরু....
ফেসবুকে মাহাবুবুল হাসান নীরু.... ইয়াহু'র আঙ্গিনায় মাহাবুবুল হাসান নীরুর বই, ভিডিও ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে ক্লিক করুন
ইয়াহু'র আঙ্গিনায় মাহাবুবুল হাসান নীরুর বই, ভিডিও ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে ক্লিক করুন মাহাবুবুল হাসান নীরুর কলাম 'বেলা অবেলা' পড়তে ক্লিক করুন
মাহাবুবুল হাসান নীরুর কলাম 'বেলা অবেলা' পড়তে ক্লিক করুন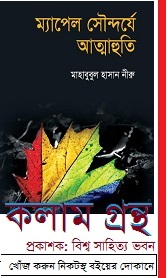 দু'হাজার এগারো সালের বইমেলায় প্রকাশিত এবং আলোচিত্ মাহাবুবুল হাসান নীরুর কলামগ্রন্থ 'ম্যাপেল সৌন্দর্যে আত্মাহুতি। প্রায় অর্ধশত কলাম সমৃদ্ধ গ্রন্থটিতে উঠে এসেছে প্রবাসী বাঙ্গালি চরিত্র এবং প্রবাস জীবনের জানা-অজানা নানা কথা। আপনি পড়ুন এবং আপনার বন্ধুকেও পড়তে বলুন...
দু'হাজার এগারো সালের বইমেলায় প্রকাশিত এবং আলোচিত্ মাহাবুবুল হাসান নীরুর কলামগ্রন্থ 'ম্যাপেল সৌন্দর্যে আত্মাহুতি। প্রায় অর্ধশত কলাম সমৃদ্ধ গ্রন্থটিতে উঠে এসেছে প্রবাসী বাঙ্গালি চরিত্র এবং প্রবাস জীবনের জানা-অজানা নানা কথা। আপনি পড়ুন এবং আপনার বন্ধুকেও পড়তে বলুন...